জুলাই ১০, ২০২৫, ০৫:৫৩ পিএম

ছবি: সংগৃহীত
ভারত-চীনের মধ্যে তিন হাজার ৪৪০ কিলোমিটার (২১০০ মাইল) দীর্ঘ এক সীমান্ত। তবে সীমান্তের এই দৈর্ঘ্যও সুনির্দিষ্ট নয়। সীমান্তে নদী, হ্রদ আর বরফে ঢাকা পর্বত থাকায় এই হিসাবে প্রায় সময় গরমিল দেখা যায়। আর এর প্রভাবে উত্তেজনা বেড়ে যায় দুই দেশের মধ্যে। অনেক সময় সীমান্তে পাহারারত দুই দেশের সেনারা পড়ে যান মুখোমুখি, কখনো কখনো তাদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনাও ঘটে। এরই এক ভয়াবহ দৃষ্টান্ত ২০২০ সালের লাদাখের সংঘর্ষ।
২০২০ সালের জুন মাসে লাদাখের গালওয়ান উপত্যকায় ভারত ও চীনের সেনাদের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের মাধ্যমে সীমান্ত সংকট চরমে ওঠে। ১৯৭৫ সালের পর দুই দেশের মধ্যে প্রথম প্রাণঘাতী সংঘর্ষ ছিল এটি। ওই ঘটনায় কমপক্ষে ২০ ভারতীয় এবং ৪ চীনা সেনা নিহত হন। এখনো লাদাখে দুই দেশের সেনাদের মধ্যে সম্পর্কের উত্তেজনা রয়ে গেছে।
এসব কারণে বছরের পর বছর চীন-ভারত সীমান্তে দেখা গেছে উত্তাপ, আর দুই দেশের কূটনৈতিক সম্পর্কে বেড়েছে শীতলতা। তবে সীমান্ত বিতর্কের মাঝেই নিজেদের সম্পর্ক নিয়ে ভাবতে বসেছে এশিয়ার দুই পরাশক্তি। গত মাসের শেষ দিকে দুই জ্যেষ্ঠ ভারতীয় কর্মকর্তার চীন সফরকে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের বরফ গলতে শুরু করার ইঙ্গিত হিসেবে দেখা হচ্ছে।
জুন মাসে সাংহাই কো-অপারেশন অর্গানাইজেশন বা এসসিও-র বৈঠকে অংশ নিতে ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল এবং প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং পৃথকভাবে চীনে যান। দশ সদস্যবিশিষ্ট ইউরেশীয় নিরাপত্তা জোট এসসিওর সদস্য দেশগুলোর মধ্যে চীন, রাশিয়া, ইরান ও পাকিস্তানও রয়েছে। চীনে রাজনাথ সিংয়ের এই সফর ছিল গত পাঁচ বছরে কোনো জ্যেষ্ঠ ভারতীয় কর্মকর্তার প্রথম সফর।
এর আগে গত বছরের শেষ দিকে লাদাখের প্রধান বিরোধপূর্ণ বিষয়গুলো নিয়ে একটি চুক্তিতে পৌঁছায় দিল্লি ও বেইজিং। চলতি বছরের জানুয়ারিতে সরাসরি বিমান চলাচল এবং ভিসা বিধিনিষেধ শিথিল করার বিষয়ে একমত হয় দুই দেশ। ২০২০ সালের সংঘর্ষের পর থেকে দুই দেশের মধ্যে সরাসরি বিমান চলাচল বন্ধ ছিল। এমনকি ভিসায় বসে কঠোর বিধিনিষেধ। পাশাপাশি প্রায় ছয় বছর পর তিব্বতের স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলে অবস্থিত তীর্থস্থান হিসেবে পরিচিত কৈলাস পর্বত ও মানস সরোবরে ভারতীয়দের দর্শনের অনুমতি দেওয়া হয়।
ভারত ও চীনের এই সম্পর্কের উন্নয়ন নিয়ে বিশ্লেষকেরা বলেন, ভূরাজনৈতিক অনিশ্চয়তা এবং বাস্তবতা দুই পক্ষকেই কিছু বিষয়ে সমঝোতার পথ খুঁজে নিতে বাধ্য করছে। তবে এখনো বেশ কিছু বড় প্রতিবন্ধকতা রয়ে গেছে।
চীন ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম বাণিজ্যিক অংশীদার। গত বছর দুই দেশের মধ্যে ১২৭ বিলিয়ন ডলারের বাণিজ্য হয়। আর ভারত চীনা আমদানির ওপর বিশেষ করে বিরল খনিজের ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল। এই প্রেক্ষাপটে সীমান্ত এলাকায় শান্তি বজায় রাখা অর্থনৈতিক সম্পর্ক জোরদারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অন্যদিকে তাইওয়ানের ওপর ক্রমবর্ধমান নজরদারি রেখেছে চীন। এর মধ্যে ভারতের সঙ্গে সীমান্তে কোনো ঝামেলায় যেতে চায় না।
পাশাপাশি চীন মনে করছে, পশ্চিমা দেশগুলো তাদের উত্থান ও প্রভাব প্রতিহত করতে ভারতকে ব্যবহার করছে। তাই সীমান্ত বিরোধ মেটানোর পাশাপাশি বেইজিং চাইছে আরও কিছু ক্ষেত্রে এগিয়ে যেতে, যাতে আমেরিকা ও তার মিত্রদের ওপর থেকে দিল্লির নির্ভরতা যতটা সম্ভব কমিয়ে আনা যায়।
এ কারণে চীন এখন ভারতে চীনা রপ্তানি বৃদ্ধির সুযোগ, চীনা বিনিয়োগ বাড়ানো এবং চীনা প্রকৌশলী ও শ্রমিকদের জন্য ভিসা বিধিনিষেধ তুলে নেওয়ার বিষয়ে আলোচনার উদ্যোগ নিচ্ছে।
এছাড়াও বিশেষজ্ঞদের মনে করছেন, দ্রুত পরিবর্তনশীল ভূরাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বিশেষ করে ডোনাল্ড ট্রাম্পের দ্বিতীয়বার মার্কিন প্রেসিডেন্ট হওয়া দিল্লিকে আবারও চীনের দিকে হাত বাড়াতে বাধ্য করেছে।
নিউ ইয়র্কের অ্যালবানি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ক্রিস্টোফার ক্ল্যারি বিবিসিকে বলেন, ‘ভারত ভেবেছিল, তারা আমেরিকার খুব ঘনিষ্ঠ কৌশলগত মিত্রে পরিণত হবে, কিন্তু ওয়াশিংটন থেকে যে ধরনের সমর্থনের আশা করছিল, তা পাচ্ছিল না।’
চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানের সঙ্গে সাম্প্রতিক সংঘাতের সময় চীন-পাকিস্তানের ক্রমবর্ধমান সামরিক সহযোগিতাও পর্যবেক্ষণ করেছে দিল্লি। চার দিনের ওই সংঘাতে পাকিস্তান ব্যবহার করেছে চীনে তৈরি যুদ্ধবিমান, আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এবং এয়ার টু এয়ার মিসাইল।
তারচেয়ে বেশি যে বিষয়টি দিল্লির ভাবনায় প্রভাব ফেলেছে সেটি হলো, এই সংঘাত নিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বক্তব্য। ট্রাম্প বারবার দাবি করেন, তিনি দুই পক্ষের (ভারত-পাকিস্তান) মধ্যে যুদ্ধবিরতির জন্য মধ্যস্থতা করেছেন। অথচ দিল্লি জোর দিয়ে বলেছিল, তারা সরাসরি পাকিস্তানের কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলে সংঘর্ষ বন্ধ করেছিল। কোনো তৃতীয় পক্ষের মধ্যস্থতার কথা তারা দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করেছিল।
এর কয়েক সপ্তাহ পর পাকিস্তানের সেনাপ্রধান আসিম মুনিরকে হোয়াইট হাউজে মধ্যাহ্নভোজে আমন্ত্রণ জানান ট্রাম্প, যা দিল্লির জন্য বেশ হতাশারই ছিল বলা যায়।
এদিকে বাণিজ্য নিয়েও দিল্লি-ওয়াশিংটন আলোচনা বেশ জটিল অবস্থায় আছে। ট্রাম্প এরমধ্যেই হুমকি দিয়েছেন, আগামী ১ আগস্টের মধ্যে কোনো চুক্তি না হলে ভারতসহ আরও কয়েকটি দেশের পণ্যে পাল্টা শুল্ক আরোপ করবেন।
অধ্যাপক ক্রিস্টোফার ক্ল্যারি বলেন, ‘ভারত-পাকিস্তান বিরোধে মধ্যস্থতার বিষয়ে ট্রাম্পের মন্তব্য এবং শুল্ক আরোপের হুমকির প্রেক্ষাপটে দিল্লির মধ্যে এখন চীনের মতো দেশের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নত করার ভাবনা তৈরি হয়েছে।’
বিশ্লেষকেরা মনে করেন, ওয়াশিংটন চীনের বিরুদ্ধে রক্ষণভাগের ভূমিকা পালনকারী হিসেবে দিল্লিকে চায়। কিন্তু ট্রাম্পের অবস্থান দেখে দিল্লির মনে এ নিয়ে সংশয়ের জন্ম হয়েছে। দিল্লি ভাবতে বসেছে, চীনের সঙ্গে ভবিষ্যতে যদি কোনো সংঘাত হয়, তাহলে আমেরিকাকে কতটা পাশে পাওয়া যাবে।
এছাড়া ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদে যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, অস্ট্রেলিয়া ও ভারতকে নিয়ে গড়ে তোলা চতুর্মুখী নিরাপত্তা সংলাপ ‘কোয়াড’ প্রায় হারিয়েই গেছে বলা চলে।
ভারতের সাবেক জ্যেষ্ঠ কূটনীতিক ফুনচুক স্তবদান বলেন, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে চীন এসসিও এবং ব্রিকসের মতো বহুপাক্ষিক সংস্থাগুলোর মধ্যে নিজেদের প্রভাব ব্যাপকভাবে বাড়িয়েছে। তাই ভারত এখন বাস্তববাদী অবস্থান নিচ্ছে।
তিনি আরও বলেন, ‘আর অভ্যন্তরীণ রাজনীতির কারণে ভারত এখন চায় না যে তাদের কোনো কাজে এটা মনে হয় যে তারা চীনের কাছে নতি স্বীকার করছে।’
অন্যদিকে চীনের সঙ্গে রাশিয়ার ঘনিষ্ঠতা বাড়ার বিষয়টিও ভারত সতর্কভাবে পর্যবেক্ষণ করছে। ইউক্রেনে হামলার পর পশ্চিমা দেশগুলোর নিষেধাজ্ঞার পর রাশিয়া চীনের ওপর আরও বেশি নির্ভর করতে বাধ্য হয়। এছাড়া রাশিয়া এখন চীন গুরুত্বপূর্ণ পণ্য আমদানি এবং বিনিয়োগের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। এ কারণে ভবিষ্যতে চীনের সঙ্গে কোনো সংঘর্ষ হলে ক্রেমলিনের অবস্থান কী হবে তা নিয়েও দিল্লি উদ্বিগ্ন।
চীন থেকে বিপুল পরিমাণে পণ্য আমদানি করা দেশগুলো এমনিতেই চাপের মধ্যে রয়েছে। এসব দেশের মধ্যে ভারতও রয়েছে। তাই দিল্লির শঙ্কা, এ ধরনের সীমাবদ্ধতা তাদের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ওপর প্রভাব ফেলতে পারে।
কূটনীতিক ফুনচুক স্তবদান বলেন, ‘চীন সম্প্রতি বাণিজ্যকে ভারতের বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে। তারা বিরল খনিজ ও সারসহ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ রপ্তানি স্থগিত করেছে। যার প্রভাব পড়ছে ভারতের উৎপাদন ও কৃষিখাতে।
গত এপ্রিল মাস থেকে চীন রপ্তানিতে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেছে। এই অবস্থায় ভারতের গাড়ি শিল্পের একটি সংগঠন সতর্ক করে জানিয়েছে, এই বিধিনিষেধ শিগগিরই শিথিল না হলে উৎপাদন মারাত্মকভাবে ব্যাহত হতে পারে। এসব উদ্বেগের প্রেক্ষাপটে, ভারত সরকার জানিয়েছে তারা বেইজিংয়ের সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে।
তবে চীন ব্যবসায়িক সম্পর্ক জোরদারে আগ্রহী হলেও, ভারতের সঙ্গে অন্যান্য ভূখণ্ডগত বিরোধে কোনো নমনীয়তা দেখায়নি। গত কয়েক বছরে উত্তর-পূর্ব ভারতের গোটা অরুণাচল প্রদেশকে নিজেদের বলে জোরালোভাবে দাবি করে আসছে চীন। বেইজিং এই অঞ্চলকে ‘দক্ষিণ তিব্বত’ বলে অভিহিত করে।
এদিকে দিল্লির পক্ষ থেকে জোর দিয়ে বলা হয়, অরুণাচল প্রদেশ ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ। রাজ্যটির জনগণ নিয়মিতভাবে ভোট দিয়ে নিজেদের সরকার নির্বাচিত করে। এ বিষয়ে কোনো ধরনের আপসের সুযোগ নেই।
সাংহাইয়ের ফুদান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শেন ডিংলি বিবিসিকে বলেন, দক্ষিণ তিব্বত না অরুণাচল প্রদেশ, যদি চীন ও ভারত যদি সার্বভৌমত্বের এই ধারণা থেকে না বেরুতে পারে তাহলে তাদের মধ্যে চিরকাল লড়াই চলবে। যদি তারা কোনো সমঝোতায় পৌঁছাতে পারে, তাহলে দুই দেশের মধ্যে চিরস্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে।
তবে দিল্লি ও বেইজিং বুঝে গিয়েছে, তাদের ভূখণ্ডগত বিরোধ শিগগিরই মীমাংসা হওয়ার নয়। তাই তারা এখন পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট একটি কার্যকর সম্পর্ক গড়ে তুলতে আগ্রহী হয়ে উঠেছে। এখন তাদের মূল লক্ষ্য হয়ে উঠেছে উত্তেজনা এড়িয়ে চলা আর কোনো বৈশ্বিক শক্তির ওপর নির্ভর না করে নিজেদের মধ্যে সমঝোতার পথেই হাঁটা।
সূত্র: আজকের পত্রিকা।

















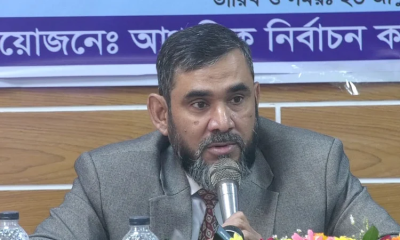





-20260210073636.jpg)





