
ছবি: সংগৃহীত
সন্জীদা খাতুনের প্রয়াণের সঙ্গে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের এক মহিরুহের শারীরিক প্রস্থান হলো। আমি জেনে-বুঝেই রাজনৈতিক ইতিহাসের কথা বলছি। রবীন্দ্রনাথের গান গাইবার জন্যও এদেশের মানুষকে যুদ্ধ করতে হয়েছে সারা পাকিস্তান আমল জুড়ে, সে শুধু এ কারণে নয় যে, একজন বিধর্মী কবির গান গাওয়ার অপরাধ, বরং আপাতদৃষ্টিতে প্রেমের কবি রবীন্দ্রনাথের গানকে এদেশের শিল্পী-সাহিত্যিক-রাজনীতিকরা বাঙালি জাতিরাষ্ট্র গঠনের কেন্দ্রে স্থাপন করেছিলেন।
আমার মনে আছে, ‘একুশের রাত’ অনুষ্ঠানে, কালেভদ্রে, বিশেষ দিবসগুলোতে, সঞ্চালনার দায়িত্ব পালন করেছি কিছুদিন। রবীন্দ্রনাথের জন্ম বা প্রয়াণ দিবসের কোনো এক অনুষ্ঠানে অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ থেকে সাংবাদিক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব কামাল লোহানী এবং অধ্যাপক সৈয়দ মঞ্জুরুল ইসলাম এবং ভারত থেকে যুক্ত হয়েছিলেন অধ্যাপক পবিত্র সরকার এবং গায়ক কবীর সুমন। ভারত থেকে যুক্ত অতিথিরা রবীন্দ্রনাথকে প্রেমের কবি হিসেবে তুলে ধরলেন এবং আমাদের অতিথিরা তুলে ধরলেন বাংলাদেশের স্বাধিকার আন্দোলনের অন্যতম প্রাণশক্তি হিসেবে।
পাকিস্তান আমলে ওয়াহিদুল হক, সন্জীদা খাতুনসহ সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বরা যে প্রবল সাংস্কৃতিক আন্দোলন করেছেন, তা ছিল সাম্প্রদায়িক, সামরিক পাকিস্তান ধারণার বিপরীতে বাঙালি সংস্কৃতি এবং বাংলাদেশ নামের রাষ্ট্রধারণার রাজনৈতিক গতিধারার অনুসঙ্গী শক্তি। রবীন্দ্রনাথকে যখন বর্জন করা হচ্ছে পাকিস্তানের রেডিওতে, টেলিভিশনে, তখন রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ঘিরেই এদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি তৈরি হচ্ছে। আস্তে আস্তেবাংলাদেশের মুখটা স্পষ্ট হয়ে উঠছে। অবয়ব পাচ্ছে ‘আমার সোনার বাংলা’। তাই অবাক হওয়ার কিছু নেই যখন ‘রক্ত করবী’ মঞ্চায়িত হচ্ছে তখন পাকিস্তানের পুলিশ এসে সেই মঞ্চায়ন ভন্ডুল করে গ্রেপ্তার করতে এসেছেন কুশীলবদের। অথচ রক্ত করবীতে তো একজন পুঁজির পাহারাদার স্বৈরাচারী রাজার বিরুদ্ধে সাধারণ জনগণের উত্থানকে দেখানো হয়েছে। সাংস্কৃতিক আন্দোলন, যে আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্ব ছিলেন সনজিদা খাতুন, ভয় পাইয়ে দিয়েছিল পাকিস্তানি শাসনব্যবস্থাকে গোটা ষাটের দশকে। এই অপরাধে অনেক বিপদে পড়তে হয়েছে সনজিদা খাতুনকে। বদলি করে দেওয়া হয়েছে বার বার। ছোট ছোট ছেলেমেয়ে নিয়ে বিপদাপন্ন হয়েছেন অসময়োচিত বদলির জন্য। মাথায় পাকিস্তানি সামরিক সরকারের খাড়া। এই ইতিহাস খুব বেশি মানুষ আর জানেনও না আজকাল। অনেকেই ছায়ানটের নাম জানেন কেবল রবীন্দ্রসংগীত শিক্ষার প্রতিষ্ঠান হিসেবে আর সনজিদা খাতুনকে চেনেন কেবল রবীন্দ্রবিশেষজ্ঞ, রবীন্দ্রসংগীত শিক্ষক এবং প্রচারক হিসেবে। এগুলোর পরিচয় সত্য।
তবে আমার কাছে ওয়াহিদুল হক, সনজিদা খাতুন, ফাহমিদা খাতুনসহ এসব প্রখ্যাত সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বদের মূল অবদান কেবল তাদের স্কলারশিপ বা শিল্পীসত্তা নয়, বরং বাংলাদেশ গঠনে তাদের নিরলস ভূমিকা এবং বাংলাদেশকে স্বরূপে রাখার জন্য তাদের অবিরাম সক্রিয়তা। শুধু রবীন্দ্রচর্চার প্রসার কিংবা স্বাধীনতার আকাক্সক্ষা জাগিয়ে তোলাই নয়, ১৯৭১ সালের ৫ মে কলকাতায় গিয়ে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে শিল্পী সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করার ক্ষেত্রে যেমন অবদান রেখেছেন সন্জীদা খাতুন, তেমনি স্বাধীন বাংলাদেশে সামরিক সরকারগুলোর আমলে বজায় রেখেছেন বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক গতিধারার মূল রূপ।
ছায়ানট, আনন্দধ্বনি, রবীন্দ্রসংগীত সম্মিলন পরিষদ, কণ্ঠশীলনের মতো একের পর এক প্রতিষ্ঠানের কাজ আমরা দেখেছি। রবীন্দ্রচর্চার পাশাপাশি নজরুল, লালন, অতুল প্রসাদ, দ্বিজেন, সত্যেন সেন এবং লোক ও গণসংগীতের চর্চা যুক্ত হয়েছে এসব পরিসরে, বিশেষ করে ছায়ানটের মধ্য দিয়ে। এই সাংগঠনিক কাজে এক সময় ওয়াহিদুল হক নেতৃত্ব দিয়েছেন, কিন্তু তার প্রয়াণের পরে মূল নেতৃত্ব সনজিদা খাতুনই দিয়েছেন। এখনো প্রতিদিন ছায়ানটে জাতীয়সংগীত বাজে। তিনি ব্রতচারী আন্দোলনের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন, যেমন যুক্ত ছিলেন পটুয়া কামরুল হাসান। ছিল উদীচীর সঙ্গে গভীর সখ্য। বাংলাদেশমুখী অনেক সাংস্কৃতিক সংগঠনের সঙ্গেই সংযোগ ছিল তার।
ব্যক্তি জীবনে, রাষ্ট্রীয় পরিসরে বড় বড় বেদনা সামলেছেন বরাবর সন্জীদা খাতুন। হয়তো সে জন্য তাকে আমরা পেয়েছি প্রগাঢ় ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, কঠোর নীতিবান একজন মানুষ হিসেবে। ২০০১ সালে ছায়ানটের বর্ষবরণে গ্রেনেড হামলার মতো ঘটনা ঘটেছে স্বাধীন দেশে। বাংলাদেশের মূল দার্শনিক অবস্থানের ক্ষয় তাকে বেদনাহত করেছে। তবে কোনো প্রতিবন্ধকতাই তাকে সাধনা থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। ব্যক্তিজীবনে ঘর ভেঙেছে, বড় মেয়ে মারা গেছেন কিন্তু তিনি কাজ করে গেছেন বাংলাদেশকে কেন্দ্রে রেখে।
তার আপাত কঠিন প্রকাশ্য ব্যক্তিত্বের ভেতরে ছিল এক দারুণ মায়াবী মন, যার প্রমাণ আমি পেয়েছিলাম অনেক বছর আগে এক সাক্ষাৎকার নিতে গিয়ে। তখন গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী আমি। আমার শিক্ষক কুররাতুল আইন তাহমিনা মিতি আপা আমাকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন সনজিদা খাতুনের সাক্ষাৎকার নেওয়ার। বাংলা বিভাগে এবং ওনার বাসায় বেশ কয়েকবার দেখা করে বেশ বড় এক সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম। সাক্ষাৎকারটা সম্ভবত বিচিন্তায় ছেপেছিলেন মিতি আপা। ওটা ছিল বিচিন্তার শেষ সংখ্যা বা শেষের দিকের সংখ্যা। ভুল হতে পারে মেনে নিয়ে আগাম ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।
ওই সাক্ষাৎকারে ওয়াহিদুল হকের সঙ্গে ঘর বাঁধার একটা ছোট বর্ণনা ছিল। বাড়ি থেকে বিয়ে ঠিক হয়ে যাচ্ছে দেখে একদিন তিনি অহিদুলের (তিনি এই নাম উল্লেখ করেছিলেন) বাড়িতে চলে এলেন। অহিদুলের মা এবং বোনেরা তাৎক্ষণিকভাবে বিয়ের ব্যবস্থা করেছেন। বোনেরা তাকে সাজিয়েছিলেন ভাঁটফুল দিয়ে। সেই ঘর টেকেনি তার। কিন্তু তখনো (নব্বইয়ের দশকের প্রথম দিকে, যখন এই সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম) বলেছিলেন, পথেঘাটে চলতে গিয়ে কোথাও ভাঁটফুল দেখলে বা ঘ্রাণ পেলে তার সেদিনের কথা চকিতে মনে পড়ে যায় কখনো কখনো। এ কথার সঙ্গে তার চোখে এক ফোঁটা জলের উদ্ভাস আমাকেও সিক্ত করেছিল। আমার সাক্ষাৎকার এখানেই শেষ করেছিলাম যতদূর মনে পড়ে।
কিন্তু অহিদুলের সঙ্গে কমরেডশিপ তার শেষ হয়নি। এদেশের সাংস্কৃতিক জগতে, রবীন্দ্রনাথসহ চিরায়ত বাংলা গান বিস্তারে এবং বাংলাদেশ ধারণাকে উজ্জীবিত রাখতে একসঙ্গে কাজ করে গেছেন দুজন আধুনিক মানুষ। মনে পড়ছে ওয়াহিদ কাকার মৃত্যুর পর ছায়ানটের দেওয়া বিদায় অনুষ্ঠানের কথা। ‘আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে’ গান গেয়ে বিদায় দিচ্ছেন সকলে। সনজিদা খাতুন এলেন মালা নিয়ে সবার সঙ্গে চোখের জলে বিদায় দিতে তার কমরেডকে। সন্জীদা খাতুনের সেই বর্ণনার পরে পথেঘাটে ভাঁটফুল দেখলে আমার তার চোখে দুফোঁটা জলের উদ্ভাস স্মরণে আসে, আর ‘আগুনের পরশমণি’ গান শুনলে ছায়ানটের ওপরতলা থেকে নেমে আসা মোমের আলোয় মোড়া সিঁড়ির নিচে রাখা ওয়াহিদ কাকার নিথর দেহ আর সন্জীদা খাতুনের ক্রন্দনরত মুখ ভেসে ওঠে।
সেদিন ওয়াহিদ কাকার বিদায় যাত্রায় যেখানে আমি ছিলাম, সেখানে পাশেই ছিলেন আবুল হাসনাত ভাই, তারিক আলী ভাই। বিশ্বাসী হলে ভাবতে ভালো লাগত এবার হয়তো তারা একত্রে আড্ডা দিচ্ছেন, গান গাইছেন, উদ্বিগ্ন হচ্ছেন বাংলাদেশ নিয়ে। কিন্তু আমার হাতে সেই জিয়নকাঠি নেই, শুধু বিশ্বাস আছে যে তাদের কাজ বৃথা হতে পারে না। সন্জীদা খাতুনের কথা বলতে গিয়ে অন্য নামগুলো আসছে বলে মার্জনা চাই। তবে তারা একেকজন অসম্ভব গুণী হওয়া সত্ত্বেও দেশের কাজে বহুজন মিলে এক হয়েছিলেন। চিন্তা ও সক্রিয়তায় তারা একতাবদ্ধ ছিলেন। তাই সন্জীদা খাতুনের সঙ্গে সঙ্গে তাদের কাজও থাকে উজ্জ্বল হয়ে কিংবা থাকে কি না তার সাক্ষ্য দেবেন যাদের শিখিয়েছেন তারা। আর সাংস্কৃতিক চর্চা কীভাবে একটি দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের দিকনির্দেশকের ভূমিকা পালন করতে পারে তার কেসস্টাডি হিসেবে ছায়ানট এবং কুশীলব হিসেবে সনজিদা খাতুন, ওয়াহিদুল হকদের ভূমিকা আমাদের পাঠ করতে হবে বারবার।
‘রবীন্দ্রসংগীতের ভাবসম্পদ’ সন্জীদা খাতুনের বই, যেটি পড়ে টেক্সট বিশ্লেষণের হাতেখড়ি হয়েছিল আমার কৈশোরে। মিডিয়া স্টাডিজের শিক্ষার্থীরা বইটি পড়তে পারেন। তার গানের কথা সবাই জানেন, সেই কথায় আর না যাই। সেই বিষয়ে লিখবেন যোগ্যতর জনরা। এই লেখাটি লিখতে লিখতে সরাসরি দেখতে পাচ্ছি ছায়ানট থেকে তাকে দেওয়া অন্তিম অভিবাদন। গানে গানে তাকে মারের সাগর পাড়ি দিতে প্রস্তুত করছেন তার স্বজনরা, এক দিন যাদের তিনি তৈরি করেছেন পরম মমতায়। সম্পর্কের পরম্পরায় তার শেখানো গান গলায় তুলে নিয়েছেন তারই শিক্ষার্থীরা। এভাবেই, সন্জীদা খাতুনের মৃত্যু হয় না। তার আদর্শেরও বিনাশ নেই যত দিন বাংলাদেশ ধারণা বহাল থাকবে। অনন্ত জেগে থাকে পরম্পরায়। তার শারীরিক বিদায়ের ক্ষণে অপার শ্রদ্ধা। বাংলাদেশ আগলে রাখুক তার যত কাজ। তাকে বোঝার মানস তৈরি হোক দেশে।
লেখক: শিক্ষক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
(মতামতটি দৈনিক দেশ রূপান্তরে পূর্বে প্রকাশ হয়েছিল)


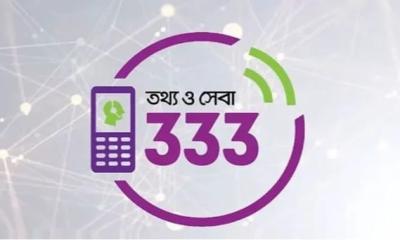












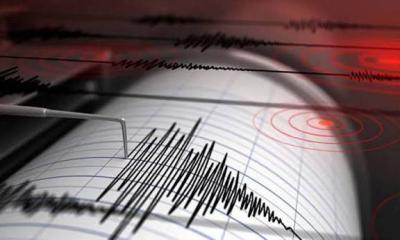












-(25)-20260203024915.jpeg)
