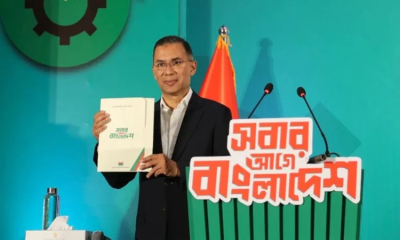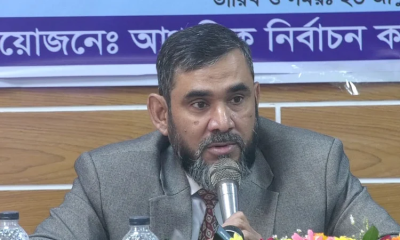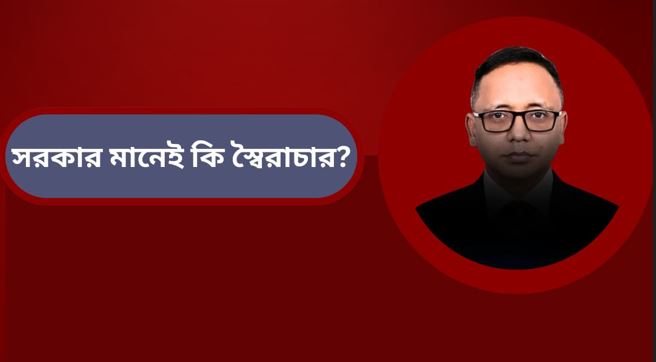
ছবি: সংগৃহীত
অন্তর্বর্তী সরকার বৈষম্যহীন বাংলাদেশ গড়ার যে অঙ্গীকার করেছিল, এক বছরের মাথায় তার উল্টো পথে হাঁটছে। অধ্যাপক আনু মুহাম্মদের সাম্প্রতিক এমন একটি মন্তব্য বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে গভীর আলোচনার জন্ম দিয়েছে। এই অভিযোগ কেবল একটি নির্দিষ্ট সরকারের প্রতি নয়, বরং বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় কাঠামো এবং ক্ষমতার চরিত্র নিয়েই প্রশ্ন তোলে।
২০২৪ সালের ৫ আগস্টের পূর্বে বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ছিল অস্থির। তৎকালীন সরকার, বিশেষ করে শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকারের বিরুদ্ধে স্বৈরাচারী আচরণের অভিযোগ ছিল ব্যাপক। দুর্নীতির বিস্তার, বিরোধী মত দমনের অভিযোগ, এবং গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের দুর্বলতা সাধারণ মানুষের মনে হতাশা সৃষ্টি করেছিল। সে সময় অনেকেই প্রত্যাশা করেছিলেন যে, একটি অন্তর্বর্তী সরকার আসার পর দেশে গণতান্ত্রিক পরিবেশ ফিরে আসবে। বৈষম্য হ্রাস পাবে এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে। বিশেষ করে, ৫ আগস্টের পর যখন শেখ হাসিনা সরকারের পতন ঘটে, তখন সাধারণ মানুষের মধ্যে নতুন এক আশার সঞ্চার হয়েছিল। ধারণা করা হয়েছিল, অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে নতুন সরকার জনগণের প্রত্যাশা পূরণে সচেষ্ট হবে।
কিন্তু অধ্যাপক আনু মুহাম্মদের ভাষ্যমতে, এই প্রত্যাশা পূরণ হয়নি। বরং, এক বছরের মাথায় অন্তর্বর্তী সরকারও পূর্ববর্তী সরকারের মতোই আচরণ করছে। তিনি সুনির্দিষ্টভাবে অভিযোগ করেছেন, এই সরকারও বৈষম্য দূর করার পরিবর্তে বৈষম্য সৃষ্টি করছে। তারাও গণতান্ত্রিক অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল নয়। এই পরিস্থিতি ইঙ্গিত দেয় যে, বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে ক্ষমতা গ্রহণের পর সরকারের চরিত্র পরিবর্তন হওয়ার একটি প্রবণতা রয়েছে। যেখানে পূর্বে উচ্চারিত বৈষম্যহীনতার বুলি কার্যত নিরুদ্দেশ হয়।
সরকার পরিবর্তন হলেও মৌলিক কাঠামোগত পরিবর্তন না আসার কারণ হিসেবে বিভিন্ন বিশ্লেষকের ভিন্ন ভিন্ন মতও রয়েছে। সাংবাদিক মোস্তফা ফিরোজ একাধিকবার তার লেখায় বা বক্তব্যে এই বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। বাংলাদেশে ক্ষমতার কেন্দ্রে যেই আসুক না কেন, রাষ্ট্রীয় আমলাতন্ত্র এবং ক্ষমতা উপভোগের যে প্রবণতা, তা প্রায় একই রকম থাকে। তিনি মনে করেন, ক্ষমতা হাতে পেলে ব্যক্তির নৈতিক অবক্ষয় ঘটে। জনগণের প্রতি দায়বদ্ধতা হ্রাস পায়। এই প্রক্রিয়াটি প্রায়শই একটি স্বৈরাচারী বা কর্তৃত্ববাদী মনোভাবের জন্ম দেয়।যেখানে সরকার নিজেকে জনগণের ঊর্ধ্বে মনে করে।
একইভাবে, সাংবাদিক মাসুদ কামাল এর মতো রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা প্রায়শই বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্রের অভাব এবং নেতৃত্বের কেন্দ্রীভূতকরণ নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। যখন একটি দলের অভ্যন্তরে গণতন্ত্রের চর্চা থাকে না, তখন সেই দল ক্ষমতায় এলে রাষ্ট্রীয় পর্যায়েও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের অভাব দেখা যায়। এই ধারা অব্যাহত থাকলে, যেকোনো সরকারই স্বৈরাচারী রূপে আবির্ভূত হতে পারে। তা যত ভালো উদ্দেশ্য নিয়েই ক্ষমতায় আসুক না কেন।
তৃতীয় মাত্রার উপস্থাপক জিল্লুর রহমান তার অনুষ্ঠানে প্রায়শই রাজনৈতিক নেতাদের দায়বদ্ধতার অভাব এবং জনগণের প্রতি উপেক্ষা নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি প্রশ্ন তোলেন যে, কেন রাজনৈতিক নেতারা ক্ষমতায় বসার আগে যে প্রতিশ্রুতি দেন, তা ক্ষমতায় আসার পর ভুলে যান? তার মতে, এর কারণ হতে পারে ক্ষমতার লোভ এবং ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করার প্রবণতা, যা বাংলাদেশে দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক সংস্কৃতির অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে।
অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ তার বক্তব্যে বিশেষভাবে শ্রেণীগত এবং লৈঙ্গিক বৈষম্যবাদের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন যে, যারা বৈষম্যবাদী দর্শন ধারণ করে, তাদের দাপট এখনকার সরকারেও দেখছেন তিনি। নারী আক্রমণকারীর দাপট এর কথা উল্লেখ করে তিনি ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, নারীদের প্রতি সহিংসতা এবং হয়রানি শুধু অতীতের সরকারের আমলেই ছিল না, বরং বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারও এটি নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। এই ধরনের অভিযোগ অত্যন্ত গুরুতর, কারণ এটি কেবল আইনের শাসন ভঙ্গুরতাকেই নির্দেশ করে না, বরং এটি সমাজের মৌলিক মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয়কেও তুলে ধরে।
অনেকেই মনে করেন যে, বাংলাদেশের সমাজে পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা এবং ক্ষমতার অপব্যবহার নারীর প্রতি সহিংসতাকে উৎসাহিত করে। যখন সরকার এই ধরনের মানসিকতার বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নেয় না, তখন এটি কেবলেই বেড়ে যায়। অন্তর্বর্তী সরকারের ক্ষেত্রেও যদি একই প্রবণতা দেখা যায়, তাহলে প্রশ্ন ওঠে, ক্ষমতার চেয়ার কি আসলেই ব্যক্তি বা দলকে নৈতিকভাবে পতন ঘটায়?
সময়ের আলোচিত আরেকজন বিশ্লেষক গোলাম মাওলা রনি। তার মতো রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা মনে করেন যে, বাংলাদেশের রাজনীতিতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূতকরণ একটি বড় সমস্যা। যখন ক্ষমতা অল্প কিছু ব্যক্তির হাতে কুক্ষিগত হয়, তখন জবাবদিহিতা কমে যায়। স্বেচ্ছাচারী মনোভাব বাড়তে থাকে। এই কেন্দ্রীভূত ক্ষমতা প্রায়শই নারী বিদ্বেষী এবং বৈষম্যমূলক আচরণের জন্ম দেয়। কারণ ক্ষমতাবান ব্যক্তিরা নিজেদেরকে আইনের ঊর্ধ্বে মনে করতে শুরু করেন।
“চেয়ারে বসার আগে যে মানুষগুলো বৈষম্যহীনতার কথা বলতেন তারা কেন আত্মসমর্পণ করলেন অথবা চুপচাপ হয়ে সরকারে আছে?” এমন প্রশ্নও তুলেছেন আনু মোহাম্মদ। তার এই প্রশ্ন বাংলাদেশের রাজনৈতিক বাস্তবতার এক কঠিন চিত্র তুলে ধরেছে। এর পেছনে বেশ কয়েকটি কারণ থাকতে পারে:
১. ক্ষমতার কাঠামোতে আত্মীকরণ: ক্ষমতায় আসার পর অনেক নেতা ক্ষমতার বিদ্যমান কাঠামো এবং ব্যবস্থার মধ্যে নিজেদেরকে মানিয়ে নিতে বাধ্য হন। এই কাঠামোতে প্রায়শই স্বৈরাচারী প্রবণতা এবং দুর্নীতি অন্তর্নিহিত থাকে। এই ব্যবস্থার অংশ হয়ে গেলে, পূর্বের আদর্শ এবং নীতি বজায় রাখা কঠিন হয়ে পড়ে।
২. রাজনৈতিক চাপ এবং আপস: নতুন সরকারগুলো প্রায়শই বিভিন্ন রাজনৈতিক চাপ, স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর প্রভাব এবং আন্তর্জাতিক শক্তির চাপ এর সম্মুখীন হয়। এই চাপ সামলাতে গিয়ে অনেক সময় তাদের নীতি ও আদর্শের সাথে আপস করতে হয়, যা তাদের পূর্বের প্রতিশ্রুতি থেকে বিচ্যুত করে।
৩. ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা: অনেক সময় ব্যক্তিগত ক্ষমতা এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষা মানুষের নৈতিকতাকে প্রভাবিত করে। যখন একজন ব্যক্তি ক্ষমতায় বসেন, তখন তার মধ্যে ক্ষমতা ধরে রাখার এবং আরও ক্ষমতা অর্জনের আকাঙ্ক্ষা দেখা দেয়। যা তাকে স্বৈরাচারী পথে ধাবিত করতে পারে।
৪. জবাবদিহিতার অভাব: বাংলাদেশে শক্তিশালী গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের অভাব এবং গণতান্ত্রিক জবাবদিহিতার দুর্বলতা স্বৈরাচারী প্রবণতাকে উৎসাহিত করে। যখন সরকার জনগণের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য হয় না, তখন তারা নিজেদের ইচ্ছামতো সিদ্ধান্ত নিতে শুরু করে। যা বৈষম্য এবং স্বৈরাচারী আচরণের জন্ম দেয়।
৫. ভয়ের সংস্কৃতি: দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক দমন-পীড়ন এবং ভয়ের সংস্কৃতি অনেক সময় সৎ ও আদর্শবান ব্যক্তিদের চুপ করে থাকতে বাধ্য করে। যদি তারা সরকারের অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বলতে যান, তাহলে তাদের ব্যক্তিগত ও পেশাগত জীবনে ঝুঁকি বাড়তে পারে।
উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে এই প্রশ্নটি ওঠে আসে যে, “তাহলে কি সরকার মানেই স্বৈরাচার?” এই প্রশ্নের সরাসরি কোনো সহজ উত্তর নেই। তবে বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা দেখে বলা যায়, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলো দুর্বল হলে, জবাবদিহিতা না থাকলে, এবং ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হলে, যেকোনো সরকারই স্বৈরাচারী আচরণ করতে পারে।
অধ্যাপক আনু মুহাম্মদের অভিযোগ এবং বিভিন্ন বিশ্লেষকের মন্তব্য এটাই প্রমাণ করে যে, সরকার পরিবর্তন হলেও ক্ষমতার চরিত্র প্রায়শই অপরিবর্তিত থাকে। এটি কেবল ব্যক্তি বা দলের দোষ নয়। বরং রাষ্ট্রীয় কাঠামোর দুর্বলতা, গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির অভাব এবং স্বার্থান্বেষী মহলের প্রভাবের ফল।
অন্তর্বর্তী সরকারের এই এক বছরের অভিজ্ঞতা আরও একবার প্রমাণ করে যে, বাংলাদেশে একটি বৈষম্যহীন ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গড়ার জন্য কেবল সরকার পরিবর্তন যথেষ্ট নয়। বরং, প্রয়োজন রাষ্ট্রীয় কাঠামোর সংস্কার, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোর শক্তিশালীকরণ, আইনের শাসনের প্রতিষ্ঠা এবং নাগরিক সমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণ।
যতদিন না এই মৌলিক পরিবর্তনগুলো সাধিত হচ্ছে, ততদিন বাংলাদেশের মানুষ স্বৈরাচারী প্রবণতা এবং বৈষম্যের শিকার হতে থাকবে। সরকার চেয়ারের যেই বসুক না কেন, যদি ক্ষমতার প্রতি জবাবদিহিতা এবং স্বচ্ছতার অভাব থাকে, তবে স্বৈরাচারী হয়ে ওঠার প্রবণতা থেকেই যায়। এই ধারা ভাঙতে হলে কেবল ব্যক্তি পরিবর্তন নয়, বরং ব্যবস্থার পরিবর্তন জরুরি।
লেখক: ফ্রিল্যান্স সাংবাদিক। abusayed.sdream@gmail.com
লেখায় প্রকাশিত মতামত লেখকের সম্পূর্ণ নিজস্ব। লেখাটি দ্য রিপোর্ট ডট লাইভের সম্পাদকীয় অবস্থানের প্রতিফলন ঘটায় না।











-20260212040742.jpeg)