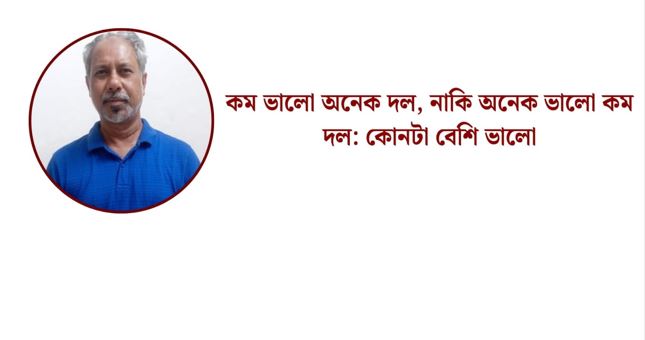
ছবি: দ্য রিপোর্ট ডট লাইভ
কেউ যদি প্রশ্ন করে একটা দেশে কতগুলো রাজনৈতিক দল থাকলে ভালো হয়? নিশ্চয়ই বলবেন এটা কোনো প্রশ্ন হলো। রাজনৈতিক দল কতগুলো থাকবে সেটা তো সেই দেশ ঠিক করবে। দলেরা ঠিক করবে আর সেটা ঠিক করবে সেই দেশের জনগণ। এটা গণতান্ত্রিক অধিকার। এটাই তো গণতন্ত্র। একটা দেশে কোন কোন রাজনৈতিক দল কিভাবে, কেন মাঠে আসবে সেই সিদ্ধান্ত তো রাজনৈতিক দলই নেবে।
রাজনৈতিক দল কতগুলো থাকবে সেটা একান্তই সেই দেশের, মানুষের, রাজনৈতিক নেতাদের নিজ্স্ব সিদ্ধান্ত। তবে বেশি দল থাকলেই সেটা গণতন্তের জন্য ভালো নাকি দল কম থাকলেও ক্ষতি নেই, সে সিদ্ধান্ত একান্তই জনতার। জনতার দল হয়ে ওঠার জন্য একটা রাজনৈতিক দলকে কেমন হতে হবে, জন মানুষের সাথে কি ধরনের আচরণ করবে সেটাও একটা প্রশ্ন।
শক্তিশালী গণতন্ত্রের জন্য দলের সংখ্যার চেয়ে তাদের কর্মকান্ড কি বেশি জরুরি নাকি দল বেশি হলেই ভালো এটা বলাও কঠিন। তবে গণতন্ত্র চর্চ্চার জন্য উন্মুক্ত রাজনৈতিক পরিবেশ, শক্তিশালী দল যে দরকার এটা নিয়ে নিশ্চয়ই কোনো শংকা নেই। সেই পরিবেশ কিভাবে তৈরি হবে, কার দায়িত্ব এসব প্রশ্নও আসে।
সব রাজনৈতিক দলই তো জনগণের প্রতিনিধিত্ব করে। দলের সিদ্ধান্ত মানেই তো জনতার সিদ্ধান্ত। জনতার সিদ্ধান্ত মানেই দলের সিদ্ধান্ত। জনতার ইচ্ছা মানেই দলের ইচ্ছা। আসলে কি তাই। জনগণ কি এসব নিয়ে কিছু করতে পারে? কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারে? জনগণের কি সেই ক্ষমতা আছে?
এ কারণেই তো এমন দল দরকার যারা জনগণের হয়ে, তাদের ভালোর জন্য সিদ্ধান্ত নেবে। তাদের মঙ্গলের জন্য কাজ করবে। সব দলই তো বলে, তারা জনতার জন্য, তাদের ভালোর জন্যই সব কিছু করছে। একমাত্র তারাই জনতার দল। এবং জনতা তাদেরই।
সংবিধানে আছে জনগণই সব ক্ষমতার উৎস। এই সত্য আসলে কতটা সত্য। বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের কোনো দেশ বা দরিদ্র কোনো দেশ, যাদের গণতন্ত্রের ঠিক নেই, খাবার কেনার টাকা নেই তারা কিভাবে কে দল করবে, কোন দল করবে কতগুলো দল থাকা উচিত হবে এই সিদ্ধান্ত নেবে। বা নিতে পারবে।
পাঁচ বছর পর পর একবার ভোট দিতে পারলেই কি ক্ষমতার অংশীদার হওয়া যায়? আবার সেই ভোটও যদি হাতছাড়া হয়ে যায় তাহলে তো আর কথাই নেই। আসলে কিভাবে বা কি করে একজন সাধারণ মানুষ তার অধিকার পেতে পারে বা ক্ষমতার উৎস বা অংশ হতে পারে তাও খুব স্পষ্ট নয়। বরং খুবই অস্পষ্ট বা অনিশ্চিত।
একটা দেশে কতগুলো দল থাকা উচিত সেই সিদ্ধান্ত কি নির্বাচন কমিশন নেবে নাকি সরকার, নাকি জনগণ। আসলে এইসব প্রশ্নের কোনো সদুত্তর নেই। তাই এসব অবান্তর। তবে বেশি দল হলে ভাল নাকি কম দল, এ প্রশ্ন তো করা যেতেই পারে। এ দেশে অনেক দল। দল নিয়েও দলাদলি অনেক, দলের ভিতরে কোন্দলও কম নয়। আবার কোন দল আসলে জনতার দল সেটা নিয়েও প্রশ্ন আছে।
একটা রাজনৈতিক দল জনগণকে কি দেয়, জনগণের জন্য কি করে। আর জনগণ একটা রাজনৈতিক দলকে কি দেয় বা দলের জন্য কি করে। এটাও নিশ্চয়ই জটিল একটা প্রশ্ন। তবে সব রাজনৈতিক দলই দাবি করে তারা জনগণের জন্য রাজনীতি করে এবং জনগণ তাদেরই পক্ষে আছে। কিন্তু জনগণ আসলে কি বলে কি চায়, কার পক্ষে সেটা রাজনৈতিক দলগুলো কি বোঝে?
একটা দলের কাছ থেকে জনগণ প্রথমত পায় প্রতিশ্রুতি। এটা করবো সেটা করবো। দেশকে স্বর্গ বানিয়ে দেব। আর সেই মালিক হবে জনগণ। তারা পায়ের উপর পা তুলে, সুখ শান্তি, সাচ্ছন্দ, স্বস্তিতে বসবাস করবে। এতটা না হলেও মানুষকে ভালো রাখার প্রতিশ্রুতি তো তারা নিশ্চয়ই দেন।
একটা দলের কর্মী হলে কি লাভ একজন সাধারণ মানুষের। ব্যক্তিগত লাভের আশায় কেউ তো রাজনীতি করেন না, দলের কর্মী হন না। তারা দেশের জন্য মানুষের জন্য রাজনীতি করতে আসেন, যে দল মানুষের প্রিয়, মানুষের জন্য কাজ করে সেই দলেরই কর্মী হতে চান। এসব কারণেই কর্মীর সাথে হয়তো নিবেদিত শব্দটি জুড়ে দেয়া হয়েছে। নিবেদনের মধ্যে শুধু দেবার আকাঙ্খাই থাকে পাবার আশা থাকে না।
একজন কর্মী দলকে সময় দেন, শ্রম দেন, ভালবাসা দেন অনেক সময় জীবনও দেন। তিনি কি পান দলের কাছ থেকে। একটা দল তাকে কি দেয়। ভালবাসা আবেগ, সম্মান, সম্পদ। অনেক সময় দল তার কর্মীকে আশ্রয় দেয়, সঙ্গ দেয় আশ্বাস দেয়, স্বপ্নের পটভূমি তৈরী করে দেয়। বাস্তবতার ভিত্তিতে তাকে দেয় সম্মান প্রতিপত্তি জনপ্রিয়তা এবং জশ। দেয় ভরসা, আশ্রয়, নিরাপত্তা।
বেশিরভাগ কর্মীই দলের কাছে কিছু চান না। তবে দলের কাছে তাদের কোনোই প্রত্যাশা নেই, প্রাপ্তির আকাঙ্খা নেই, তাও কিন্তু নয়। প্রাপ্তিরও একটা বিষয় আছে। কখনও সেটা প্রকাশ্য কখনো প্রচ্ছন্ন। তবে সেই আকাঙ্খা খুব বেশী কিছু নয়। আর সেই আকঙ্খার অনেক কিছুই মেলে না দিনশেষে। মেলে হতাশা। তারপরও দল ছেড়ে যেতে চায় না একজন কর্মী। দল কিছু দিক না দিক তবুও এটাই তার দল।
একজন কর্মী দলের জন্য কাজ করে। আরো কর্মী যোগার করে, টাকা যোগান দেয়। দলকে রক্ষার জন্য কাজ করে। শ্লোগান দেয়, মিছিল করে। দলের জন্য পুলিশের মার খায়, বাসায় গিয়ে বকা খায়। দলের জন্য যা কিছু প্রয়োজন তাই করে। দলের জন্য কাজ করা্তেই তার আনন্দ, এটাই তার প্রাপ্তি।
এসবের বিনিময়ে অনেক সময় দলের কাছ থেকে কিছু সাহায্য সহযোগিতা, কখনো কখনো কিছু টাকা পয়সা পেয়ে থাকে কর্মীরা। কেউ কেউ সেটা নেয় অনেকেই নেয় না। বড় কর্মসূচী থাকলে খবার দাবারও মেলে। আবার অনেক সময় খরচও করতে হয় একজন কর্মীকে।
কর্মীদের বড় একটা আশা থাকে দল ক্ষমতায় গেলে তার জন্য কিছু একটা করবে। ভালো কিছু। তাকে ক্ষমতার ভাগ দেয়া, পোস্ট-পোজশিন দেয়া। টাকা কামানোর উপায় করে দেয়া। বিশেষ করে তাকে ক্ষমতাবান করে তোলা। কিন্তু তা কি সব সময় হয়? অনেক ক্ষেত্রেই হয় না। সেজন্য নেতা হতে হয়। আর খুব অল্প সংখ্যক কর্মীই তো নেতা হবার সূযোগ পান।
বেশীর ভাগ কর্মীই কিছু পাননা। আসলে একজন নিবেদিত প্রাণ কর্মী তার নেতার জন্য দলের জন্য যা করেন একটা দল কি তার কিয়দংশও তার জন্য করে। দলের কাছ থেকে কি পাওয়া গেল সেই হিসাব হয়তো অনেক কর্মীই করেন না। নেতারা দল বদল করেন, কর্মীরা নয়। করলেও সেই সংখ্যা হয়তো খুবই নগণ্য।
অনেক কর্মীই তার দল নির্বাচন করেন নেতা দেখে। নেতার কর্মকান্ডে মুগ্ধ হয়ে, নেতার আদর্শে উব্দুদ্ধ হয়ে। দেশের জন্য নেতার নিবেদন দেখে। আর যারা কিছুই দেখ বা না দেখে দল করেন তারাই শেষ পর্যন্ত হেরে যান কিংবা হারিয়ে যান। অনেকেই মনে করেন তাদের আশা পূরণ হয় না। হয়তো জনতারই দোষ, তারা বড় বেশী আশা করে।
আর দল যখন ক্ষমতায় থাকে না তখন জনগণের অধিকা্র আদায়ের আন্দোলন করে। সংসদে বিরোধী দল হিসাবে থাকলে জনগণের সমস্যা তুলে ধরে। তাতে জনগণের কি খুব বেশি কিছু লাভ হয়। দল ক্ষমতার বাইরেই থাক আর ক্ষমতায়ই থাকে তাতে সাধারণ মানুষের খুব বেশি কিছু লাভ হয় না। জনতা আশায় আশায় থাকতে থাকতে একসময় হতাশ হতেও ভুলে যায়।
প্রায় সব কর্মীরই আশা থাকে তিনি একদিন বড় নেতা হবেন, তার কথা সব কর্মীরা শুনবে। কারণ নেতা না হতে পারলে কেউ কথা শোন না, দলের কাছ গুরুত্ব থাক না। যার কর্মী সংখ্যা যত বেশি তিনি তত বড় নেতা। কিন্তু সেটা সব সময় হয়ে উঠে না। যার টাকা বেশি, পেশী শক্ত, যাত পিছ যত লোক, তিনি তত বড় নেতা হয়ে ওঠেন। দলের ভিতরেই শুরু হয় নোংরা প্রতিযোগিতা।
কে কত বড় নেতা, কার কত প্রতিপত্তি, কার কথায় বেশী লোক আসে, কার নামে বেশি শ্লোগান হয় সেই প্রতিযোগিতা চলে। ধীরে ধীরে দলের ত্যাগী নিবেদিত নেতা কর্মীরা হেরে যান, হারিয়ে যেতে থাকেন বা পিছনে চুপচাপ বসে থাকেন।
দলে কর্মী এবং সমর্থকের সংখ্যা যত বেশি হবে সেই দলই তো বড় দল হবার কথা। কিন্তু ব্যক্তিগত লাভালাভ যখন বড় হয়ে ওঠে তখন আরেক ধরনের বাস্তবতা সামনে চলে আসে। মিডিয়ায় চেহারা দেখানো দলের শীর্ষ নেতাদের নজর কাড়ার চেষ্টা, বেশি বেশি টাকা খরচ করার প্রবণতা, নেতাদের উপঢৌকন এসব অনেক বিষয় তখন বড় হয়ে ওঠে আরো নগন্য হয়ে যান প্রকৃত নেতা কর্মীরা।
তখন দলের ভিতরেই শুরু হয়ে যায় দ্বন্দ্ব আর অন্য দলের সাথে অসম প্রতিযোগিতা। এই দ্বন্দ্বের বলী হন নিবেদিত রাজনৈতিক কর্মীরা লাভবান হন সূযোগ সন্ধানীরা আর ক্ষতিগ্রস্ত হয় রাজনীতি। এই ক্ষয় ধীরে ধীরে ধ্বংস করে দিতে পারে একটি রাজনৈতিক দলকে।
কর্মীভিত্তিক বা ক্যাডার ভিত্তিক রাজনৈতিক দলের চর্চ্চা কিন্তু খানিকটা ভিন্ন। সেই সব দলে একজন রাজনৈতিক কর্মীকে একটা প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে গড়ে তোলা হয়। কখনো কখনো বেশ দীর্ঘ এবং কঠিন হয় সেই প্রক্রিয়া। কর্মীকে দলের আদর্শ এবং নীতি কঠোর ভাবে মেনে চলতে হয়। এর বাইর যাওয়াও অনেক ক্ষেত্রে কঠিন হয়ে ওঠে।
আদর্শভিত্তিক রাজনৈতিক দল। সব দলেরই তো একটা আদর্শ থাকে। তবে এখন অনেক দলের মূল আদর্শ ক্ষমতায় যাওয়া। এটাকে বলা যায় ক্ষমতাভিত্তিক রাজনীতি বা ক্ষমতার জন্য রাজনীতি। Power politics. আবার ক্যাডারভিত্তিক রাজনীতিরও উদ্দেশ্য ক্ষমতায় যাওয়া। সব দলই কারণ দেখায় ক্ষমতায় না গেলে আদর্শ প্রতিষ্ঠা করা যায় না। জনগণকে ক্ষমতায়িত করা যায় না।
হয়তো অনেকেই আর মানুষের মুক্তির জন্য রাজনীতি করে না, করে নিজের মুক্তির আশায়। ক্ষমতার লোভ আরা টাকার ভাবাসায়। আর এ কারণেই একটা দল তৈরী করে ফায়দা লুটতে চায়। হয়তো এ ধরনের লোক বা দলের সংখ্যা খুবই নগন্য, কিন্তু নেই কি বলা যাবে।
এ ধরনের দল বেশি হলে জনগণের মঙ্গল তো নেইই বরং ক্ষতি। কর্মীরাও অনেকে দলে আসেন শুধু আখের গোছাাতে। সেই সংখ্যাও নেহাত কম নয়, বা বলা যেতে পারে এখন বেশীরভাগেরই এই উদ্দেশ্য। যার আরেকটা প্রতিশব্দ ধান্দা। ধান্দা থকে ধান্দাবাজী। কখনো কখনো ধান্দাই সব কিছু ছাপিযে সব চাইতে বড় হয়ে ওঠে।
রাজনীতির ধরণ পাল্টেছে সেই সাথে রাজনৈতিক দলের কাঠামো আচরণ সব প্রায় সব কিছু। এ কারণেই হয়তো এখন নীতি আদর্শ, দেশ প্রেমের চেয়েও ক্ষমতায় যাওয়া এবং টিকে থাকার বিষয়টি অনেক বেশী গুরুত্বপূণূ হয়ে উঠেছে। ক্ষমতাকে নিজের মত করে ব্যবহার করা, টাকা বানানোর মাধ্যম করে তোলা। আর এসব কারণে রাজনীতির ধরনের সাথে সাথে নেতাকর্মীদের আচরণও পাল্টে যাচ্ছে।
রাজনীতি, দল, নেতাকর্মী সবারই একমাত্র লক্ষ্য ক্ষমতাকেন্দ্রিক রাজনীতি। দল ক্ষমতায় থাকুক বা বাইরে থাকুক, কেন্দ্রবিন্দু কিন্তু একটাই, ক্ষমতা। এখন প্রশ্ন হচ্ছে ক্ষমতা ছাড়া কি মানুষের সেবা করা যায় না, দেশের ভালো করা যায় না। ক্ষমতা ছাড়া কি রাজনীতি বা দল হয় না। কিন্তু ক্ষমতা ছাড়া তো টাকা বানানো যায় না, আর টাকা ছাড়া তো ভালো কিছু করা যায় না।
দেশের জন্য মানুষের জন্য, দলের কর্মীদের জন্য, একটা দলকে ক্ষমতায় যেতেই হবে। কিন্তু ক্ষমতায় গেলে তো দলগুলো, যে মানুষের কাধে ভর করে ক্ষমতায় যায়, তাদের কথাই ভুলে যায়। তখন আর তাদের কাছে সেইস সব মানুষের কোনো মূল্যই থাকে না। সরকার আর দল ভিন্নসত্বা হয়ে ওঠে, কর্মীরা হয়ে ওঠেন গৌণ, অপাঙতেয়। মূল্যবান জনতার কোনো মূল্য থাকে না মূল্যায়ণ তো দূরের কথা।
রাজনৈতিক দলের সংখ্যাও বেশি হবার কারণে যারা দলকে ব্যবহার করতে চান তাদের হয়তো সুবিধা কিছুটা বাড়ে কিন্তু সাধারণ মানুষের কি খুব বেশি লাভ হয়। সবাই ক্ষমতায় যাবার কথা বলে বা স্বপ্ন দেখিয়ে রাজনৈতিক দল তৈরি করে, সুবিধা নেয়ার চেষ্টা করে। দেশ বা জনগণের চাইতে দল এবং ব্যক্তির স্বার্থ তাদের কাছে বড় হয়ে ওঠে। অনেক ক্ষেত্রেই রাজনীতিবিদরা যা বলেন কার্যত ঘটে তার উল্টোটা।
সারা বছর ধরে যারা রাজনৈতিক দলের সাথে থাকেন তারা কিন্তু বেশিরভাগই কর্মী। তারা দলকে ভালোবেসে দেশের জন্য কিছু একটা করার জন্যই দলের কাছে আসেন। করার চেষ্টাও করেন। সেটা কতটা ফলপ্রসু হয় সেটা নির্ভর করে দলের উপর, এর দায় তো কর্মীর নয়।
দলের বিভিন্ন কর্মসূচির সময় যখন বেশি লোক সমাগমের দরকার হয়, তখন সমর্থকরা আসেন আর সেই সাথে ভাড়া করা লোকদেরও নিয়ে আসা হয়। ভাড়া করা লোকরা শুধু টাকার জন্যই আসেন, সে কারণেই যারা বেশি টাকা দেয় তারা সেখানেই যান। তাদের কাছে দল বেশি হলে লাভ দর কষাকষরি সূযোগ বাড়ে। আয়ও বাড়ে। এক দল ছেড়ে আরেক দলে যাওয়ার সূযোগও আসে।
রাজনৈতিক কর্মসূচি থাকলে কর্মীরাও অনেক সময় কিছু টাকা পান, খাবার দাবার পান। সমর্থক সংগ্রহের সূযোগ পান। তবে প্রকৃত কর্মীরা এসবের জন্য কাজ করেন না, কিছুই চান না, পান ও না। তারা নিঃস্বার্থ ভাবেই দলের জন্য কাজ করে যান, শেষ পর্যন্ত হয়তো কিছুই পান না, উপেক্ষা আর অবহেলা ছাড়া। তারপরও দলের দুঃসময়ে এরাই থাকেন অন্যদের খুঁজেও পাওয়া যায় না।
দল ক্ষমতায় গেলেও সেটা দলের জন্য অনেক সময় ক্ষতির কারণ হয়ে দাড়ায়। ক্ষমতার দুর্নাম দলের উপর আসে। দলের জনপ্রিয়তা কমে আসে। দল থেকেও থাকে না, আবার দল ছাড়াও চলে না। চল চালাবার মত লোকবল বা আগ্রহ কোনোটাই থাকে না। সেটাও এক ধরনের জটিলতা। এসব জটিলতা কিভাবে দূর করা যাবে সেটাও একটা ভাবনার বিষয়।
যদি সত্যিকার অর্থে দলের ভিতরে এবং সার্বিক ব্যবস্থা্য় গণতন্ত্রের চর্চা থাকে তবে হয়তোবা কিছু সমস্যার সমাধান মিলতে পারে। দলগুলো যখন সুযোগ সুবিধার আধারে পরিণত হয় তখন দলের সংখ্যা বাড়াবার প্রবণতাও বাড়ে। যত দল, তত বল, তত বেশি কৌশল।
নির্বাচনের সময় দল নিয়ে আরেক ধরনের দলবাজি শুরু হয়। বড় দলগুলো ছোট দলগুলোক কাছে টানার চেষ্টা করে, অনেক ধরনের জোট তৈরি হয় ভোটের জন্য। সেটা নিয়ে দর কষাকষি জোট ভারি করার চেষ্টা। এইসব ঘটনাগুলো এ দেশের রাজনৈতিক পক্ষোপটে ঘটেছে এবং ঘটে যাচ্ছে। এসব কমবেশি সবাই জানে এবং বোঝে। কিন্তু তাতে অবস্থার খুব বেশি পরিবর্তন হয়নি। পরিস্থিতি দিন দিনই খারাপ থাকে আরো খারাপ হচ্ছে। Going bad to worse.
রাজনৈতিক অঙ্গনে খুব বেশি পরিবর্তন আশা কেউ করে না। সবাই জানে ভোটের আগে এসব ঘটবে। এর থেকে কে কত বেশি ফায়দা লুটতে পারে সেটাই তাদের দেখার বিষয়। কিন্তু দলগুলো ভোটারদের অধিকার রক্ষার জন্য কতটুকু আন্তরিক, কতটা কাজ করছে বা করবে সে বিষয় নিয়ে ভাববার খুব বেশি অবকাশ হয়তো থাকে না।
তারমানে রাজনৈতিক দল হলেই হবে না তাকে অবশ্যই জনগণের বা গণ-মানুষের দল হয়ে উঠতে হবে। কিন্তু সাধারণ মানুষ সব সময় সেই আস্থা রাখতে পারে না। তারা বিপন্ন, বিচ্ছিন্ন বোধ করে, কখনো কখনো অসহায়। রাজনৈতিক দলের আচরণ সাধারণ মানুষের কাছে অচেনা মনে হয়। দলগুলো আসলে তাদের নিয়ে কি ভাবছে কি করছে সেটা তারা হয়তো সব সময় বুঝে উঠতে পারে না।
সুতরাং দল সংখ্যায় বেশি হলেই যে সেটা জনগণের জন্য ভালো, তা নাও হতে পারে। দল জনপ্রতিনিধিত্বশীল না হলে, সত্যিকার অর্থেই জনমানুষের না হলে কিছই যায় আসে না। এ সবই আপেক্ষিক একটা কথা, জনপ্রতিনিধিত্বশীলার মাপকাঠিই বা কি। সব সময়ই সেটা জনপ্রয়িতা বা ভোটের সংখ্যা দিয়ে কি মাপা যাবে?
বহু দল থাকা আর বহুদলীয় গণতন্ত্র কিন্তু এক জিনিস নয়। অবশ্যই দল করার অধিকার সবার থাকবে। অনেক দল থাকবে। সবারই দল করার স্বাধীনতা থাকবে। কিন্তু দল করার বেশ কিছু যোগ্যতাও থাকতে হবে। সেই যোগ্যতার মাপকাঠি ঠিক করবে নির্বাচন কমিশন। সব শর্ত পূরণ করতে পারলেই দেয়া হবে নিবন্ধন, সেই সাথে রাজনৈতিক কর্মকান্ড চালানোর অধিকার।
অনেক দেশই আছে যেখানে রাজনৈতিক দলের সংখ্যা সীমিত। কোথাও কোথাও দুই বা তিনটা। গণতন্ত্রের বিচারে সেই সব দেশের অনেকগুলোই বেশ এগিয়ে। অনেক ভালো গণতন্ত্রের দেশে দুই দলের সংখ্যাই বেশি। তাতে গণতন্ত্র বা রাজনৈতিক চর্চার কোনো বিঘ্ন ঘটছে না।
তবে উন্নয়নকামী বা দরিদ্র দেশগুলোতে রাজনৈতিক দলের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশি। কোনো দেশে এমনকি ভারতেও সেই সংখ্যা অনেকটাই বেশি। তবে তাদের দলের চর্চ্চার মধ্যে শৃঙ্খলা আছে। আবার সংখ্যা কম নিয়েও শৃঙ্খলা আনতে পারেনি সেই রকম দেশের সংখ্যাও কম নয়।
বাংলাদেশে নির্বাচন কমিশনে নিবন্ধিত দলের সংখ্যাও পঞ্চাশের বেশি। আরো বেশ কয়েকটি দল নিবন্ধন পেতে যাচ্ছে। কাউকে কাউকে আবার বাদ দেয়ার চেষ্টাও চলছে। এর বাইরেও অনেকগুলো দল আছে। এখানে অনেক দলেরই ৩০০ আসন কেন ১০০ আসনে মনোনয়ন দেয়ার মত লোক নেই, অফিস নেই, নির্দিষ্ট কর্মকান্ড নেই, তারপরও দল ঠিকই আছে।
নিবন্ধন নেই, জনসমথর্নও নেই, সাংগঠনিক কাঠামো বা কার্যক্রম কিছুই নেই, কিন্তু দল আছে। দল থাকা কোনো অসুবিধার বিষয় নয়, তবে কি কারণে তারা আছে সেটা মানুষের কাছে প্রমাণ করার প্রয়োজনীয়তাও নিশ্চয়ই আছে। দলের সংখ্যা নয় একেকটি দল জনগণের জন্য কি করছে কতটা ফলপ্রসু ভূমিকা রাখতে পারছে সেটাই বিবেচ্য। সংখ্যার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ আদর্শ, উদ্দশ্যে এবং কাজের পরিধি এবং ধরণ।
দল শুধুই মানুষের ভালোর জন্য কাজ করে যাচ্ছে, তবে মানুষ মনে করে আখের গোছানো বা স্বার্থসদ্ধি ছাড়া আর কোনো কাজই তারা করে না। তারপরও সাধারণ মানুষেরর ভরসাও কিন্তু রাজনৈতিক দলই। শেষ পর্যন্ত তারাই তাদের সবকিছু ত্রাণদাতা এবং কর্তা। অনেক দল থাকলেও হাতে গোনা কয়েকটা দলের সাথেই জড়িত অধিকাংশ মানুষ।
রাজনৈতিক দলের একমাত্র এবং শক্তিশালী অভিভাবক হবে নির্বাচন কমিশন। দেখভাল থকে শুরু করে তাদের অর্থ সংস্থান, পরিচালনা পদ্ধতি সব বিষয়েই সহযোগিতা করবে নির্বাচন কমিশন। নিয়ন্ত্রণ নয় সহযোগিতা। শর্তভিত্তিক সহযোগিতা।
একটি পরপিূর্ণ প্রকৃত রাজনৈতিক দলই পাবে সব ধরনের সাহায্য ও সহযোগিতা। এই সহযোগিতা কোনোভাবেই নিয়ন্ত্রণ নয়। দল দলের মতই চলবে, তবে নিবন্ধনের জন্য তাকে বেশ কিছু শর্ত কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে। মেনে চলার মধ্য দিয়ে দলগুলো আরো পরিণত, জনপ্রিয়, জনবান্ধব এবং গণতান্ত্রিক এবং শক্তিশালী হয়ে উঠবে। আর যত দল বেশি গণতান্ত্রিক হবে তত বেশি শক্তিশালী।
জোর করে বা বলপূর্বক কোনো দলকে আবদ্ধ বা নিষিদ্ধ করা যাব না, দলের স্বাধীন কর্মকান্ডে বাধা দেয়া যাবে না। তবে নিয়ন্ত্রক সংস্খা নির্বাচন কমিশনকে যথেষ্ট শক্তিশালী বিচক্ষণ ও কার্যকরী ভূমিকা রাখার মত স্বক্ষম হতে হবে। নিয়ন্ত্রণ মানে তাকে দমিয়ে রাখা বা বিলুপ্ত করে দেয়া নয়, দলকে শক্তিশালী ও গণতান্ত্রিক এবং সত্যিকার অর্থেই গণমানুষের হয়ে গড়ে উঠতে সহায়তা করা।
কঠিন শর্ত দিয়ে তাকে অবরুদ্ধ বা বাধাগ্রস্থ নয়, বরং তার বিকাশের পথকে সচল এবং সুগম করে তোলা। দলের কাঠামো কার্যক্রম এবং দল পরিচালনার খরচের বিষয়ে সহায়তা করা। দলের গঠন প্রক্রিয়া, এবং কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কঠোর শর্ত দেয়া এবং সেটা মানিয়ে চলার মত পরিস্থিতি তৈরি করা।
কোনো দলই pro-country, pro-liberation and nationalism এর বাইরে যেতে না পারে সেই শর্তগুলো দলকে মেনে চলার মত পরিবেশ সৃষ্টি করা। সবই দলের রক্ষা এবং বিকাশের স্বার্থে করতে হবে। নিয়ন্ত্রণ নয় নিয়ম মেনে চলতে বাধ্য করা। শর্ত মানলেই পাওয়া যাবে এবং থাকবে নির্বাচন কমিশনের নিবন্ধন্ন। সুস্থ রাজনৈকিত চর্চ্চা, শক্তিশালী রাজনৈতিক দল এবং গণতন্ত্রের বিকাশের জন্য এসবের একান্ত্র প্রয়োজন। অনেক দল নয়, দরকার গণ-মানুষের দল, গণতান্ত্রিক দল।
লেখক: লেখক, গবেষক, সাংবাদিক।
· লেখায় প্রকাশিত মতামত লেখকের সম্পূর্ণ নিজস্ব। লেখাটি দ্য রিপোর্ট ডট লাইভের সম্পাদকীয় অবস্থানের প্রতিফলন ঘটায় না।




















-20260125111950.jpeg)


-20260126111852.jpg)
-20260127113058.jpg)




