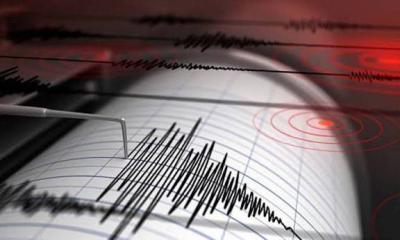ফেব্রুয়ারি ৭, ২০২৩, ০৮:২৬ পিএম

শক্তিশালী ভূমিকম্পে প্রায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে তুরস্ক ও সিরিয়ার বেশ কয়েকটি প্রদেশ। দুই দেশে এ পর্যন্ত পাঁচ হাজারের বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে। প্রতিনিয়ত বেড়ে চলেছে মৃত্যুসংখ্যা। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার মতে, দুই দেশের প্রায় ২ কোটি ৩০ লাখ মানুষ ভূমিকম্পের শিকারে পরিণত হয়েছে। ভূমিকম্পের এই ভয়াবহতায় দুশ্চিন্তা বাড়ল ঢাকারও। যদিও ওই ভূমিকম্পের প্রভাবের কারণে নয়, বরং দীর্ঘদিন ধরেই ঢাকা ভূমিকম্পের সবচেয়ে ঝূঁকিতে রয়েছে। ভূমিকম্প বিশেষজ্ঞদের মতে, একটি অঞ্চলে একটি বড় ভূমিকম্প হওয়ার একশ বছর পর কাছাকাছি যে কোনো সময় আবার বড় ভূমিকম্প আঘাত হানে। বাংলাদেশে ১৯১৮ সালে বড় ধরনের ভূমিকম্প হয়েছিল। সে হিসেবে ২০১৮ সাল পেরিয়ে গেছে। এখন যে কোনো সময় বড় ভূমিকম্প হতে পারে।
ঢাকা শহরে জনবসতির ঘনত্ব বেশি হওয়ায় শক্তিশালী ভূমিকম্পের কবলে পড়লে মহাদুর্যোগ হয়ে যাবে। ধ্বংসস্তূপের নিচে পড়ে যত মানুষ মারা যাবে, তার কয়েক গুণ মারা যাবে আগুনে পুড়ে ও বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে। কারণ ভূমিকম্পের পর গ্যাসের লাইনের পাইপে বিস্ফোরণ ঘটবে আর সেই আগুনে পুরো নগর দাউ দাউ করে জ্বলবে। এর নিয়ন্ত্রণ বা উদ্ধার অভিযান কল্পনাও করা যাবে না। কারণ, ইতিমধ্যে তাজরিন ফ্যাশনস, র্যাংগস ভবন দুর্ঘটনাসহ ছোটখাট কিছু ঘটনায় উদ্ধার অভিযানের দুর্বলতা আন্দাজ করা গেছে। র্যাংগস ভবন ভাঙতে গিয়ে অনেকের প্রাণ গেছে। এক শ্রমিকের লাশ (আসলে কঙ্কাল) কংক্রিটের ছাদে ঝুলেছিল ঘটনার পাঁচ মাস পরও!
বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ভূমিকম্পের মতো দুর্যোগে বিশ্বের অন্যতম ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলে পড়েছে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা। ঘনবসতির এই শহরটির ঝুঁকি কমাতে এ পর্যন্ত বিভিন্ন প্রকল্প ও পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কথা বলা হলেও তার বেশিরভাগই আলোর মুখ দেখেনি।
আর্থ অবজারভেটরি সেন্টারের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ইন্ডিয়ান, ইউরেশিয়ান এবং বার্মা, এই তিনটি প্লেটের সংযোগস্থলে বাংলাদেশের অবস্থান। যা বড় ধরনের ভূমিকম্পের ঝুঁকি সৃষ্টি করতে পারে।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূ-তত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক সৈয়দ হুমায়ুন আক্তার এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, সাধারণত প্রতি ১০০ বছর পর বড় ধরনের ভূমিকম্প হয়ে থাকে। সবশেষ ১৮২২ এবং ১৯১৮ সালে মধুপুর ফল্টে বড় ভূমিকম্প হয়েছিল। সে হিসেবে আরেকটি বড় ভূমিকম্পের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে বাংলাদেশ। আর দেশের মধ্যে সবচেয়ে ঝুঁকিতে রয়েছে ঢাকা।
অপরিকল্পিত এই শহরের ভবনগুলো বানানো হয় যথাযথ নিয়ম (বিল্ডিং কোড) না মেনে। সেক্ষেত্রে ভূমিকম্প অসহনশীল ভবনগুলো চিহ্নিত করে সেগুলো সংস্কার বা ধ্বংস করার পরিকল্পনা করা হলেও তার কোনো বাস্তবায়ন নেই। যখনই বিশ্বের কোথাও ভূমিকম্প হয়, তখনই কর্তাব্যক্তিরা একটু নড়েচড়ে বসেন। কিন্তু সময়ের ব্যবধানে সেই উদ্যোগ আলোর মুখ দেখে না।
বিশেষজ্ঞদের মতে, সবচেয়ে বড় দুর্বলতার জায়গা হলো বিল্ডিং কোড অনুযায়ী ভবন নির্মাণ না করা এবং সেগুলো মনিটর করে কোন ব্যবস্থা না নেওয়া।
পুরকৌশলবিদরা বলছেন, ঢাকায় ঝুঁকিপূর্ণ ভবনের সংখ্যা প্রতিনিয়ত বাড়ছে, তার সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে ভূমিকম্পে দুর্যোগের ঝুঁকিও। ঢাকার ঘিঞ্জি এলাকা থেকে শুরু করে অনেক অভিজাত এলাকার বহুতল ভবন পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখা গেছে, এগুলোর বেশিরভাগই উচ্চমাত্রার ভূমিকম্প সহনশীল নয়। কারণ এগুলো বিল্ডিং কোড লঙ্ঘন করেছে। চিলি ও হাইতির ভূমিকম্পের ক্ষয়ক্ষতির পরিসংখ্যান থেকে দেখা গেছে, চিলিতে ভবনগুলো যথাযথ নিয়ম মেনে তৈরি ছিল বলে ক্ষতি কম হয়েছিল। কিন্তু হাইতির চিত্র ছিল পুরোটাই উল্টো।
এ ক্ষেত্রে ঢাকার ঝুঁকিপূর্ণ ভবনগুলো চিহ্নিত করে সেগুলো গুঁড়িয়ে ফেলা কিংবা ভূমিকম্প সহনশীল করে সংস্কার করা প্রয়োজন হলেও তার কোনো ক্ষেত্রেই অগ্রগতি হয়নি। ফলে ভূমিকম্প হলে ভূগর্ভস্থ পানি ও আশপাশের নদী-জলাশয়ের পানিতে নগরে অকস্মাৎ বন্যার সৃষ্টি হবে। উপড়ে পড়া বিদ্যুতের খুঁটির তারের সংস্পর্শে এসে পানিতে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হবে। সেই পানিতে পড়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মারা যাবে লাখো মানুষ।
যদি তেমন কিছু ঘটে, মিয়ানমারের আরাকান এলাকায় ৮ দশমিক ৬ মাত্রার ভূমিকম্প হতে পারে। সেই কম্পন ঢাকায় ৯ তীব্রতার অনুভূত হতে পারে। সে ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিকভাবে ঢাকা ও চট্টগ্রামের ৭২ হাজার ভবন ভেঙে পড়বে। টাঙ্গাইলের মধুপুরে ৭ দশমিক ৫ মাত্রার ভূমিকম্প হলে ঢাকায় তা ৯ তীব্রতার অনুভূত হবে। ঢাকা শহরের ৩৫ ভাগ মাটি লাল। এই মাটির ওপর তৈরি ভবনের ক্ষয়ক্ষতি কম হবে। ৬৫ ভাগ মাটি নরম। ভূমিকম্প হলে নরম মাটির ওপর কম্পনের স্থায়িত্ব বেশি হবে এবং ক্ষয়ক্ষতিও বেশি হবে।
ঢাকায় বড় ধরনের ভূমিকম্প হলে তাতে আধঘণ্টার মধ্যে উদ্ধারকাজ শুরু করা গেলে ৯০ শতাংশ মানুষকে বাঁচানো যাবে। উদ্ধারকাজ শুরু করতে এক দিন লাগলে ৮১ শতাংশ, দুদিন লাগলে ৩৬ শতাংশ এবং তিন দিন লাগলে ৩৩ শতাংশ মানুষকে উদ্ধার করা সম্ভব হবে। উদ্ধারকাজ শুরু করতে যত বেশি বিলম্ব হবে মৃতের সংখ্যা তত বেশি বাড়বে।
ভূমিকম্প হওয়ার সাথে সাথে করণীয় সম্পর্কে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, কেন্দ্রীয়ভাবে বিদ্যুৎ ও গ্যাসের সরবরাহ বন্ধের ব্যবস্থা থাকতে হবে। একই সাথে উদ্ধারকাজ চালানোর জন্য যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং জরুরি ভিত্তিতে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে।
বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করে বলছেন, কয়েক বছর আগে নেপালে যে ভূমিকম্প হয়, তখন সেখানকার বাসাবাড়িতে গ্যাসের সিলিন্ডার ব্যবহার হওয়ার কারণে ক্ষয়ক্ষতি অপেক্ষাকৃত কম হয়েছে। ঢাকায় যে পরিমাণ গ্যাসের পাইপ লাইন ও রাসায়নিকের মজুত আছে, তাতে শহরজুড়ে আগুন জ্বলবে। নগরে বন্যার সৃষ্টি হবে। বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মানুষ মারা যাবে। শহর অন্ধকারে ডুবে যাবে। ভূমিকম্প মানুষ মারে না। মানুষ মরে মানুষের তৈরি অব্যবস্থাপনার কারণে। ভূমিকম্পের বিপর্যয় মোকাবিলায় বিল্ডিং কোড মেনে ভবন তৈরি করতে হবে। ঢাকার ৭৬ শতাংশ সড়ক সরু। এগুলো প্রশস্ত করতে হবে।
বড় সংকট হলো, ঢাকায় বড় ধরনের ভূমিকম্প হলে আক্রান্ত মানুষকে উদ্ধারের লোক খুঁজে পাওয়া যাবে না। উদ্ধারে যারা মূল ভূমিকা রাখবে সেই ফায়ার সার্ভিসের অস্তিত্ব থাকবে কি না, তা নিয়েও সন্দেহ আছে জনমনে।















-20251209075227.jpeg)