নভেম্বর ২৩, ২০২৫, ০৪:৩৮ পিএম

ভূমিকম্পকে আমরা সাধারণত আকস্মিক কাঁপুনি হিসেবে অনুভব করি। সহজভাবে বললে, ভূমিকম্প হলো পৃথিবীর ভেতরের বড় বড় খণ্ড বা টেকটোনিক প্লেটগুলোর হঠাৎ গতিবিধি পরিবর্তন বা পিছলে যাওয়া। এই পিছলে যাওয়ার ফলে যে বিপুল পরিমাণ শক্তি বেরিয়ে আসে, সেই চলে আসা শক্তিই মূলত পৃথিবীর উপরিভাগে কাঁপুনির সৃষ্টি করে।
ফল্ট, হাইপোসেন্টার ও এপিসেন্টার কি
ফল্ট প্লেন (Fault): যে তল বরাবর পাথরের ব্লক বা টেকটোনিক প্লেটগুলো একে অপরের থেকে সরে যায় বা পিছলে যায় তা ফল্ট প্লেন নামে পরিচিত।
হাইপোসেন্টার (Hypocenter): পৃথিবীপৃষ্ঠের নিচে যেই বিন্দু থেকে বা যে স্থান থেকে ভূমিকম্পের উৎপত্তি হয়, সেটিকে বলা হয় হাইপোসেন্টার বা ভূমিকম্পের কেন্দ্র।
এপিসেন্টার (Epicenter): হাইপোসেন্টারের ঠিক উপরে বা ভূমিকম্পের কেন্দ্রের ঠিক ওপরে থাকা স্থানটিকে এপিসেন্টার বা উপকেন্দ্র বলা হয়। এখানেই আমরা সবচেয়ে বেশি কাঁপুনি অনুভব করি।
ভূমিকম্পের কারণ
পৃথিবীর চারটি প্রধান স্তর রয়েছে।
১.অন্তঃস্থ কেন্দ্র (Inner Core)
২.বহিস্থ কেন্দ্র (Outer Core),
৩.ম্যান্টল (Mantle) ও
৪.ভূত্বক (Crust)
পৃথিবীর একদম কেন্দ্রে আছে কঠিন অন্তঃস্থ কেন্দ্র বা `ইনার কোর`।
তাকে ঘিরে আছে তরল বহিস্থ কেন্দ্র বা `আউটার কোর`।
আর আমরা বাস করি একদম বাইরের পাতলা আর ভঙ্গুর স্তরটার ওপর, যেটাকে বলে `ভূত্বক` বা `ক্রাস্ট`
ম্যান্টেলের ওপরের অংশ আর ভূত্বক, এই দুটো মিলে পৃথিবীর পৃষ্ঠে তৈরি হয়েছে একটি পাতলা স্তর, যাকে বলা হয় `লিথোস্ফিয়ার` (Lithosphere)। এই স্তর একক কোনো খণ্ড নয়। এটি পৃথিবীপৃষ্ঠকে আবৃত করে থাকা বিশাল বিশাল কিছু ভাঙা টুকরো দিয়ে গঠিত। এসব টুকরাকে বলে টেকটোনিক প্লেট।
এসব প্লেটের কিনারাকে বলা হয় প্লেট বাউন্ডারি। প্লেট বাউন্ডারি অনেক চ্যুতি নিয়ে গঠিত। প্লেটের কিনারাগুলো রুক্ষ হয়। আর এই প্লেটগুলো কিন্তু স্থিরও নয়, এগুলো সারাক্ষণ নড়াচড়া করছে। নড়াচড়ার ফলে প্লেটের কিনারাগুলো পরস্পরের সঙ্গে আটকে যায়। যখন প্লেট যথেষ্ট দূরে সরে যায়, তখন চ্যুতির মধ্যে থাকা কিনারা আলাদা হয়ে ভূমিকম্প হয়। বিশ্বের বেশিরভাগ ভূমিকম্প প্লেটের সীমানায় ঘটে থাকে।
এই প্লেটগুলো তিনভাবে নড়াচড়া করে:
১. মুখোমুখি (Convergent Boundary)— যখন দুটো প্লেট মুখোমুখি ধাক্কা খায় তাকে বলে `কনভার্জেন্ট বাউন্ডারি`, এর ফলে মারাত্মক শক্তিশালী ভূমিকম্প হয়। আর এই ভূমিকম্পের ফলে বড় বড় পাহাড় তৈরি হতে পারে।
২. বিচ্ছিন্ন (Divergent Boundary) — আবার যখন দুটো প্লেট একে অপরের থেকে দূরে সরে যায় তাকে বলে `ডাইভার্জেন্ট বাউন্ডারি`, তখন তুলনামূলক ছোট আকারের বা হালকা ভূমিকম্প হয়।
৩. পাশাপাশিভাবে ঘর্ষণ (Transform Boundary)— যখন প্লেটগুলো পাশাপাশি একে অপরকে ঘঁষে চলতে থাকে তখন সবচেয়ে বেশি বিপজ্জনক পরিস্থিতি তৈরি হয়। এটাকে বলে `ট্রান্সফর্ম বাউন্ডারি`। এই ঘর্ষণের ফলে প্রচণ্ড শক্তি জমা হয় আর হঠাৎ বড় ভূমিকম্প হতে পারে।
প্রশ্ন হলো ঠিক কোন মুহূর্তে আর কেন এই কাঁপুনিটা তৈরি হয়
প্লেটের সীমানায় এর এবড়োখেবড়ো ধারগুলোর ঘর্ষণের কারণে একে অপরের সাথে আটকে যায়। কিন্তু প্লেটের বাকি অংশ তো থামে না, সেটা চলতেই থাকে। ফলে ওই আটকে থাকা জায়গায় প্রচণ্ড চাপ তৈরি হতে থাকে। এই পুরো প্রক্রিয়াটাকে বিজ্ঞানীরা বলেন `ইলাস্টিক রিবাউন্ড`। ব্যাপারটা অনেকটা রাবার ব্যান্ড টানার মতো। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই জমানো সমস্ত শক্তি একসাথে বেরিয়ে আসে। যে শক্তিটা বেরিয়ে আসে, এটা ঠিক যেন পুকুরে ঢিল ছুঁড়লে যেমন ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে, সেভাবেই ভূগর্ভের ভেতর দিয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। অর্থাৎ ওই শক্তি তরঙ্গ আকারে ছড়িয়ে পড়ে। এই তরঙ্গগুলোকেই আমরা বলি `সিসমিক ওয়েভস` (Seismic Waves)। এটাই যখন ভূপৃষ্ঠে এসে পৌঁছায় তখন আমরা কাঁপুনিটা অনুভব করি।
কিন্তু বিজ্ঞানীরা এই অদৃশ্য তরঙ্গগুলোকে কীভাবে শনাক্ত করেন ? মানে ভূমিকম্পের কেন্দ্রটা তারা খুঁজে বের করেন কীভাবে?
ভূমিকম্পের শক্তি ছড়িয়ে পড়ে মূলত কয়েক ধরনের সিসমিক ওয়েভের মাধ্যমে। এর মধ্যে সবচেয়ে আগে আসে `পি-ওয়েভ` (P-wave), `এস-ওয়েভ` (S-wave) তারপর সারফেস ওয়েভ (Surface wave)।
P-wave (প্রথম সংকেত) -পি-ওয়েভ কঠিন-তরল সবকিছুর মধ্য দিয়ে যেতে পারে
S-wave (দ্বিতীয় সংকেত)- এস-ওয়েভ শুধু কঠিন পদার্থের মধ্য দিয়ে যেতে পারে
পি-ওয়েভ দ্রুত গতিতে আগে এসে পৌঁছায় আর মাটি প্রথমবার কাঁপে। ঠিক যেমন আমরা মেঘ ডাকার শব্দের আগেই বিজলির ঝলকানি দেখতে পাই তেমন। পি-ওয়েভ ও এস-ওয়েভের এক জায়গায় এসে পৌঁছানোর সময়ের যে পার্থক্য, সেটাই বিজ্ঞানীদের ভূমিকম্পের উৎসটা কত দূরে তা মাপতে সাহায্য করে।
আর দূরত্ব বের করার পর সঠিক জায়গা জানার জন্য বিজ্ঞানীরা ব্যবহার করেন `ট্রায়াঙ্গুলেশন` (Triangulation) পদ্ধতি।
ভূমিকম্পের মাত্রা কীভাবে রেকর্ড করা হয়
ভূমিকম্পের সময় P-wave, S-wave আর Surface wave নামে যে তিন ধরনের কম্পন তৈরি হয় সেগুলো সিসমোমিটার নামের এক বিশেষ যন্ত্র সেই কম্পনগুলোকে গ্রাফ আকারে রেকর্ড করে—যাকে বলা হয় সিসমোগ্রাম।
আগে রিখটার স্কেল ব্যবহার করা হতো, কিন্তু এখন Moment Magnitude Scale Mw সবচেয়ে বেশি নির্ভরযোগ্য।
বিজ্ঞানীরা কি ভূমিকম্পের পূর্বাভাস দিতে পারেন
উত্তরটা খুবই স্পষ্ট — না। নির্ভুলভাবে সময়, স্থান ও মাত্রা - ভূমিকম্পের আগাম পূর্বাভাস দেওয়া এখনও সম্ভব নয়। বিজ্ঞানীরা ভূমিকম্পের পূর্বাভাস দেওয়ার জন্য অনেক রকম পদ্ধতি নিয়েই গবেষণা করেছেন। কিন্তু কোনোটাতেই এখনো নির্ভরযোগ্যভাবে সাফল্য আসেনি।
তবে সম্ভাব্য ঝুঁকি মূল্যায়ন (Forecast / Hazard Assessment) সম্ভর
তাঁরা বলতে পারেন—
কোন অঞ্চল বেশি সক্রিয়
প্লেট সীমান্ত কোথায়
কত বছরে বড় ভূমিকম্প ঘটতে পারে
কোন ভবন কাঠামো ঝুঁকিতে
ভূমিকম্প শুরু হওয়ার পর P-wave শনাক্ত করে কিছু দেশে ৫–৩০ সেকেন্ড আগে (Early Warning) সতর্ক বার্তা দেওয়া হয়। এটা পূর্বাভাস নয়, বরং তাৎক্ষণিক সতর্কতা।





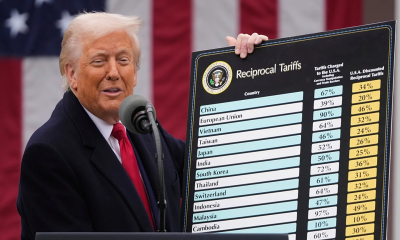








-20260220111935.jpeg)











-20260216100616.jpg)


