
ছবি: সংগৃহীত
চলতি বছরের প্রথম ছয় মাসে বিশ্ববাজারে ডলারের যে পতন হয়েছে, তা ১৯৭৩ সালের পর সবচেয়ে বড় ধস। যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান বাণিজ্য অংশীদার দেশগুলোর মুদ্রার বিপরীতে ডলারের মান কমেছে ১০ শতাংশের বেশি।
যুক্তরাষ্ট্র মুদ্রা ছাপানোর ক্ষেত্রে স্বর্ণমান থেকে বেরিয়ে আসার পর ১৯৭৩ সালে ডলারের বড় ধরনের দরপতন হয়েছিল। স্মরণে রাখা দরকার, ওই সিদ্ধান্ত ছিল যুগান্তকারী ঘটনা। এরপর বৈশ্বিক আর্থিক ব্যবস্থায় ডলারের ব্যবহার ও মান বেড়ে যায়।
এবারের পটভূমি ভিন্ন। এখন ডলারের এই পতনের পেছনে আছে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিশ্বব্যবস্থাকে পুনর্গঠনের প্রচেষ্টা, বিশেষ করে আগ্রাসী শুল্কনীতি ও আত্মকেন্দ্রিক পররাষ্ট্রনীতি। ট্রাম্পের শুল্কনীতি, মূল্যস্ফীতির আশঙ্কা ও সরকারি ঋণের বাড়বাড়ন্ত—সব মিলিয়ে ডলারের ওপর চাপ সৃষ্টি হচ্ছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আন্তর্জাতিক আর্থিক ব্যবস্থায় যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃস্থানীয় ভূমিকায় বিনিয়োগকারীদের ক্রমেই আস্থা কমে আসা।
ডলারের দাম কমে যাওয়ায় মার্কিন নাগরিকদের বিদেশে ভ্রমণের খরচ বেড়েছে। সেই সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রে বিদেশি বিনিয়োগ কমে যাচ্ছে। এমন এক সময়ে বিষয়টি ঘটছে, যখন দেশটি আরও বেশি ঋণ নেওয়ার চেষ্টা করছে।
অন্যদিকে ডলার দুর্বল হওয়ায় মার্কিন রপ্তানিকারকদের সুবিধা হয়েছে, যদিও আমদানির খরচ বাড়ছে। কথা হচ্ছে, মুদ্রা দুর্বল হলে স্বাভাবিকভাবে এসব ঘটে। কিন্তু প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের শুল্ক আরোপের হুমকির কারণে বাণিজ্যসংক্রান্ত এই ‘স্বাভাবিক’ বিষয়গুলোও অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।
তবে যতই দিন যাচ্ছে, ততই ট্রাম্পের শুল্ক আরোপের হুমকি ক্ষীণ হচ্ছে। অর্থাৎ নীতিগতভাবে ট্রাম্প সেই অবস্থান থেকে কিছুটা সরে এসেছেন। এই পরিস্থিতিতে মার্কিন শেয়ারবাজার চাঙা, বন্ডের বাজারও ঘুরে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু ডলারের মান কমেই চলেছে।
এই পরিস্থিতিতে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ডের বিদেশি মুদ্রা গবেষণা বিভাগের স্টিভ ইংল্যান্ডার বলেন, ‘ডলার দুর্বল, না শক্তিশালী, এটা মূল প্রশ্ন নয়। মূল প্রশ্ন হলো, বিশ্বসমাজ তোমার অবস্থান কীভাবে দেখছে?’
ট্রাম্প পুনর্নির্বাচিত হওয়ার পরপর ডলার ঊর্ধ্বমুখী ছিল। বিনিয়োগকারীদের ধারণা ছিল, ট্রাম্প ব্যবসাবান্ধব ও প্রবৃদ্ধিমুখী। এমনকি যুক্তরাষ্ট্রে বিনিয়োগ করা হলে বিপুল সুবিধা দেওয়া হবে বলেও ঘোষণা দিয়েছিলেন। ফলে ধারণা করা হয়েছিল, ট্রাম্প বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে পারবেন এবং পরিণতিতে ডলারের চাহিদা বাড়বে।
কিন্তু সেই আশা স্থায়ী হয়নি। জানুয়ারির মাঝামাঝি সময় অর্থাৎ ট্রাম্পের শপথ গ্রহণের সময় ডলার সূচক সর্বোচ্চ জায়গায় পৌঁছার পরই পড়তে শুরু করে। নতুন প্রশাসন ব্যবসাবান্ধব হবে, সেই আশা দূর হয়ে শুরু হয় উচ্চ মূল্যস্ফীতির আতঙ্ক, উচ্চ সুদহারের দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব আর অর্থনীতি ও শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানিগুলোর ওপর নেতিবাচক প্রভাবের শঙ্কা।
এরপর আসে ট্রাম্পের ঘোষিত সেই ‘স্বাধীনতা দিবস’ অর্থাৎ ২ এপ্রিল, যেদিন তিনি পাল্টা শুল্ক আরোপের ঘোষণা দেন। সেদিন তিনি একেবারেই অপ্রত্যাশিত উচ্চ হারে শুল্ক আরোপের ঘোষণা দেন; যে বিষয়টি অর্থনীতিবিদ, বিনিয়োগকারী কিংবা বিশ্লেষক—কেউই অনুমান করতে পারেননি। ফলে শেয়ারবাজার থেকে শুরু করে বন্ডের বাজার ও ডলার—সব ক্ষেত্রেই আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।
বিনিয়োগকারীরা শঙ্কিত, এ ধরনের শুল্ক–সৃষ্ট মূল্যস্ফীতির কারণে সুদের হার দীর্ঘ মেয়াদে আরও বেড়ে যেতে পারে। মার্কিন অর্থনীতিতে এমনিতেই দুর্বলতার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে, সেই পরিস্থিতিতে অর্থনীতি আরও বিপদের মুখে পড়বে।
এই পতনের শুরুটা ট্রাম্প প্রশাসনের শুল্কনীতির মধ্যে নিহিত। ট্রাম্প প্রশাসন যখন শুল্ক আরোপের সিদ্ধান্তে অনড় অবস্থান নেয়, তখন শুধু মূল্যস্ফীতি নয়, পুরো বৈশ্বিক অর্থনীতি নিয়ে শঙ্কা আরও গভীর হয়। একসময় বিষয়টি ছিল মূল্যস্ফীতি ও শ্রমবাজার নিয়ে দুশ্চিন্তা। পরবর্তী সময়ে পুরো মার্কিন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার স্থিতিশীলতা নিয়েই প্রশ্ন ওঠে।
বিশ্লেষকেরা বলছেন, বিশ্বজুড়ে বিনিয়োগকারীরা এখন ধীরে ধীরে ডলার ও যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক সম্পদের বিকল্প খুঁজছেন। যদিও অনেক দিন ধরে বৈশ্বিক বিনিয়োগের নিরাপদ গন্তব্য ছিল যুক্তরাষ্ট্র।
বছরের শুরুতে অবশ্য ডলারের মান ভালোই ছিল। সে কারণে চলতি বছরের শুরুটা যতটা খারাপ হোক, ঐতিহাসিক দিক থেকে ডলার এখনো অতটা দুর্বল নয়। স্টিভ ইংল্যান্ডার আরও বলেন, এত দিন জনমনে ধারণা ছিল, মার্কিন অর্থনীতি ‘ব্যতিক্রমধর্মী’, কিন্তু এখন সেই ব্যতিক্রমধর্মিতা হারিয়ে যাচ্ছে। ফেডারেল রিজার্ভের চেয়ারম্যানের সঙ্গে ট্রাম্প যে আচরণ করছেন, তাতে পরিস্থিতির অবনতিই ঘটছে বলে মনে করছেন বিনিয়োগকারীরা।
বিষয়টি হলো, শুল্ক বাড়লে আমদানি কমে আর আমদানি কমলে বিদেশি ব্যবসায়ীদের ডলারভিত্তিক লেনদেন কমে যায়। ফলে সেই ডলার আবার যে যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে আসবে, সেই সম্ভাবনা কম, বিশেষ করে সরকারি বন্ডের বাজারে। একদিকে মুদ্রা বিনিময়ের ঝামেলা, অন্যদিকে মার্কিন অর্থনীতির ওপর আস্থার ঘাটতি—দুটিই একসঙ্গে কাজ করছে।
বিনিয়োগের অনুসন্ধান
এই বছরের মতো ডলারের পতনের নজির কমই আছে। ১৯৭৩ সালের পর প্রথমবার এমন পতনের মুখে পড়ে ডলার। সে বছর বিশ্বের বড় অর্থনীতির দেশগুলো ডলারের সঙ্গে মুদ্রা বিনিময়ের হার বেঁধে রাখার পদ্ধতি থেকে সরে এসেছিল। সেটা ঘটেছিল প্রেসিডেন্ট নিক্সনের স্বর্ণমানের সঙ্গে ডলারের সম্পর্ক ছিন্ন করার দুই বছর পর।
এদিকে ডলারের এই দুর্বলতার কারণে শেয়ারবাজারে চাঙা ভাবের পুরো ফল পাওয়া যাচ্ছে না। বিনিয়োগকারীদের মুনাফায় প্রভাব পড়ছে। এসঅ্যান্ডপি ৫০০ সূচক যখন ২৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে নতুন রেকর্ড গড়েছে, তখন ইউরোয় হিসাব করলে সেই মুনাফা দাঁড়াচ্ছে মাত্র ১৫ শতাংশ—সর্বোচ্চ অবস্থান থেকে ১০ শতাংশ নিচে।
এই পরিস্থিতিতে অনেক মার্কিন বিনিয়োগকারী এখন দেশের বাইরের দিকে ঝুঁকছেন। ইউরোপের শেয়ারবাজার সূচক ইউরোস্টক্স ৬০০ একই সময়ে ১৫ শতাংশ বাড়লেও ডলারে রূপান্তর করলে তা ২৩ শতাংশে উঠেছে। বড় বড় পেনশন তহবিল থেকে শুরু করে ট্রাস্টি প্রতিষ্ঠানগুলো বলছে, তারা এখন যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে আরও ভালো বিনিয়োগের সুযোগ খুঁজছে।
ঘাটতি ও ঋণ বাড়ছে
শুল্কের কারণে মার্কিন সম্পদের প্রতি আগ্রহ কমার এই সময় মার্কিন সরকার ব্যয় বাড়ানোর পরিকল্পনা করছে। অথচ ট্রাম্পের খরচ কমানোর নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ছিল।
সিনেটের কিছু বিরোধিতা সত্ত্বেও বিলটি আবার কংগ্রেসে উঠেছে। অনুমান করা হচ্ছে, এই বিল পাস হলে আগামী এক দশকে কয়েক ট্রিলিয়ন ডলারের ঘাটতি তৈরি হবে।
এই ঘাটতি পুষিয়ে নিতে সরকারকে ট্রেজারি থেকে আরও বেশি ঋণ নিতে হবে। কিন্তু এখানেই মূল সংকট—যাদের কাছ থেকে এই ঋণ নেওয়া হবে, তারাই এখন মার্কিন বাজার থেকে দূরে সরে যাচ্ছেন। ফলে প্রশ্ন উঠছে, ট্রেজারি ও ডলার আদৌ আর ‘নিরাপদ আশ্রয়’ হিসেবে কাজ করছে কি না।
অস্থিরতার সময় বিনিয়োগকারীরা সাধারণত স্থিতিশীল সম্পদে বিনিয়োগ করেন। কিন্তু বর্তমানে ডলার নিয়ে যে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে, তাতে এই মুদ্রা আরও দুর্বল হচ্ছে।
ডিডলারাইজেশন
রাশিয়া–ইউক্রেন যুদ্ধের সময় যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়ার ওপর শত শত নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। এর মধ্যে ছিল ডলারে রাশিয়ার লেনদেন বন্ধ করে দেওয়া এবং রাশিয়ার সম্পদ জব্দ করা। তার প্রতিক্রিয়ায় অনেক দেশই ভাবতে শুরু করে, তাদেরও এ রকম পরিস্থিতির শিকার হওয়ার অবকাশ আছে। ডলারকে এভাবে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার কেউই ভালো চোখে দেখেনি। ফলে অনেক দেশই ডলার ভিন্ন অন্য মুদ্রায় লেনদেন বৃদ্ধি করে, যাকে বলা হয় ডিডলারাইজেশন।
যদিও বিশ্লেষকেরা বলেন, সম্পূর্ণ ডিডলারাইজেশন এখনো বহুদূরের বিষয়। যে বিষয়টি প্রকৃত অর্থেই মাথাব্যথার কারণ হয়ে উঠছে, তা হলো ক্রমবর্ধমান সরকারি ঋণ।


















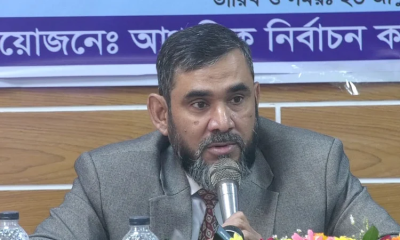






-20260210073636.jpg)



